|
|
|
|
|
|
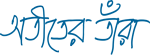 |
| তিন গুণের আধার |
পরিব্রাজক, সাংবাদিক, লেখক। এই তিনের ভিতরে আটকে রাখা না-গেলেও
মূলত এই পরিচয়েই তিনি আপামর বাঙালির কাছে বন্দিত। তাঁর নামকরণ
করেছিলেন এমন এক জন মানুষ, যিনি ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’র সম্পাদক।
কাগজটির নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে আবেগ ও নিষ্ঠা তার বাহক হিসেবে তো
বটেই লেখালেখি ও নানা পত্রপত্রিকা পরিচালনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন জলধর সেন। |
 |
|
“আমি যেদিন জন্মগ্রহণ করলুম, সেদিন বাবা আর জেঠামশাই দুই হাতে পয়সা খরচ করেছিলেন। কাঙ্গালীও যথেষ্ট বিদায় করেছিলেন। ছেলে ভবিষ্যতে কাঙ্গাল হবে এই কথা ভেবেই বোধ হয় তাঁদের সেদিন দুঃখী কাঙ্গালীর খবর নিতে ইচ্ছে হয়েছিল। তবে শুনেছি এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন আমার জীবনপথের পথপ্রদর্শক হরিনাথ মজুমদার যিনি বাঙ্গালীর নিকট ‘কাঙ্গাল হরিনাথ’ নামে পরিচিত। এ-ও শুনেছি সাধক হরিনাথ বাড়ির সকলকে বলেছিলেন, এ ছেলে যেদিন আঁতুড় থেকে বেরুবে, সেদিন কেউ একে আগে কোলে করতে পারবে না, আমি কোলে নেব। তাঁর আদেশ কেউ অমান্য করেনি। তিনিই প্রথম কোলে নিয়েছিলেন এবং নামকরণ করেছিলেন।”— জলধর সেন।
সংক্ষিপ্ত জীবনী
১৩ মার্চ, ১৮৬০ (১ চৈত্র ১২৬৬) নদিয়ার কুমারখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন জলধর সেন। পিতা হলধর সেন। জলধরের যখন তিন বছর বয়স, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। জলধরের কথায়, “পিতার মৃত্যুর পরে আমরা শুধু পিতৃহীন হলাম না, পথের ভিখারী হয়ে পড়লুম।”
এর পর শিক্ষাজীবন শেষ করে, ১৮৮৫ সালে গোয়ালন্দ স্কুলে শিক্ষকতা করাকালীন তিনি বিবাহ করেন সুকুমারীদেবীকে। বিবাহ সম্পর্কে জলধর সেন তাঁর স্মৃতিতর্পণে বলেছেন, “সেই যে ৮১ অব্দে পঁচিশ টাকা বেতনে শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত আমার সে মাইনে আর বাড়েনি। ঐ সালের শেষ ভাগে স্কুলের কর্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তাঁরা আমার বেতন ৫ টাকা বাড়িয়ে দিলেন। ...আমার এ বেতন বৃদ্ধির কারণ এই যে স্কুল কর্তৃপক্ষ নানা ভাবে জানতে পেরেছিলেন যে আমাদের দরিদ্র সংসারে আর একটি লোক বৃদ্ধি হয়েছে। সেই নবাগত লোকটির খোরাকি বাবদ তাঁরা আমার ৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি করে দেন। সে নবাগত আর কেহ নন আমার স্ত্রী।”
১৮৮৭ সালটি জলধরের জীবনে বড় দুঃসময়। জন্মের বারো দিনের মাথায় মারা যায় তাঁর শিশুকন্যাটি। তারও বারো দিন পর দেহত্যাগ করেন সুকুমারীদেবী। এর তিন মাস পরে জলধরের মাতৃবিয়োগ হয়। সংসার-দুঃখে কাতর জলধর অধীর চিত্তকে সংযত করতে জন্মভূমি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন হিমালয়ের উদ্দেশে। নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে শেষে তিনি পৌঁছলেন দেরাদুনে। সেখান থেকে বদ্রিকাশ্রম।
বিপত্নীক জলধরকে সংসারী করার জন্য বন্ধুরা উঠেপড়ে লাগল। এবং ১৮৯৩ সালে, উস্তির দত্ত পরিবারের হরিদাসীদেবীর সঙ্গে তাঁর পুনর্বিবাহ হয়।
শিক্ষা ও কর্মজীবন |
 • ছেলেবেলায় বঙ্গ বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা। হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। • ছেলেবেলায় বঙ্গ বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা। হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।
• ১৮৭১ সালে গোয়ালন্দ স্কুল থেকে মাইনর পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি লাভ। ১৮৭৮-এ কুমারখালি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে থার্ড গ্রেড জুনিয়র স্কলারশিপ পান।
• এর পরের বছর জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। কিন্তু এল এ পরীক্ষা দিলেও পাশ করতে পারেননি। তবে চাকরি পেতে কোনও অসুবিধে হয়নি। গোয়ালন্দ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন পঁচিশ টাকা বেতনে।
• ১৮৯১-৯২ সালে চল্লিশ টাকা বেতনে মহিষাদল রাজ স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। মহিষাদলে থাকতেই তাঁর হিমালয় ভ্রমণ কাহিনি ‘ভারতী’, ‘সাহিত্য’ ও ‘জন্মভূমি’তে ক্রমে প্রকাশিত হয়।
• প্রায় ৮ বছর মহিষাদলে শিক্ষকতার করার পর ‘বঙ্গবাসী’ সাপ্তাহিক পত্রে সম্পাদকীয় বিভাগে কাজের দায়িত্ব পান। মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে।
কিন্তু ‘বঙ্গবাসী’র মূলমন্ত্র মেনে নিতে না পারায় মাত্র দেড় মাস সাহিত্যসেবায় থেকে তা ছেড়ে দেন।
• এর পর দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর যুক্ত ছিলেন ‘ভারতববর্ষ’ পত্রিকার সম্পাদনায়।
কাঙাল হরিনাথ ও জলধর সেন
জলধরের কথায়, “হরিনাথ আমার শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, আমার জীবনের আদর্শ।”
কাঙাল হরিনাথের ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে হরিনাথের অন্যান্য সহযোগীদের মধ্যে জলধর যেমন অনন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, তেমনই হরিনাথের ‘ফিকিরচাঁদ’-এর বাউলসঙ্গীত দল গঠনেও মুখ্য ভূমিকা ছিল তাঁর। গান গেয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে হাজার হাজার মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করার কাজে হরিনাথের ছায়াসঙ্গী ছিলেন জলধর।
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও জলধর সেন
কাঙাল হরিনাথের বহু শিষ্যের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও জলধর সেন। স্কুলে শিক্ষকতার সময় জলধরের কয়েকটি লেখায় সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। জলধরের এই অনুরাগ যাতে ছাত্র পড়িয়ে নষ্ট না হয় সেই চেষ্টা করতেন বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।
সে সময় প্রায় প্রতি দিন বিদ্যাসাগরমশাইয়ের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বাড়িতে সাহিত্য সম্মেলন বসত। সেখানে আসতেন রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নবীনচন্দ্র সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু, অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। জলধরকে সেই সাহিত্য-তীর্থে নিয়ে গেলেন অক্ষয়কুমার। তাকে সাহিত্য সাধনার সুযোগ দানের যে চেষ্টা হচ্ছিল তা সফল হয়। প্রধানত ‘সাহিত্য’ পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্রের চেষ্টায় তিনি ‘বসুমতী’ সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। |
 |
শান্তিনিকেতনের রবিবাসরে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ৩০ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মন্মথনাথ ঘোষ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে জলধর সেন। |
রজনীকান্ত সেন ও জলধর সেন
তখন তিনি
বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক। ‘‘তখন স্বদেশীর বড় ধূম। এক দুপুরে আমি বসুমতী আফিসে বসে আছি, এমন সময় রজনী (রজনীকান্ত সেন) ও রাজশাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এসে উপস্থিত। রজনী সেই দিনই দার্জিলিং মেলে বেলা এগারোটা নাগাদ কলকাতায় পৌঁছে অক্ষয়কুমারের মেসে উঠেছিলেন। মেসের ছেলেরা জেদ ধরেছেন একটি গান লিখে দেওয়ার জন্য। গানের নামে রজনী পাগল হয়ে যেতেন। গানের মুখরা ও একটি অন্তরা লিখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সকলে গান শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। বললেন, ‘এই তো গান হইয়াছে, এ বার জলদা’র কাছে যাই। একদিকে গান কম্পোজ হউক, আর একদিকে লেখা হউক।’ আমি দেখে বললাম, আর কই? রজনী বলিল, ‘এইটুকু কম্পোজ কর, বাকিটুকু হইয়া যাইবে।’ সত্যি কম্পোজ আরম্ভ হইল আর অন্য দিকে গান লেখাও শেষ। আমি আর অক্ষয় সুর দিলাম। গান ছাপা হয়ে এল। এই গান ঘিরে ছেলেদের মধ্যে সেকি উন্মাদনা! স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ গানটি সর্বজনমনে স্পর্শ করে গেল।” এটি জলধরের নিজের কলমেই লেখা। এবং ইতিহাস খ্যাত সেই গানটি হল,
‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়...’।
বিদ্যাসাগর ও জলধর সেন
গণিতের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল জলধরের। ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হবেন। কিন্তু কলকাতায় থেকে জীবনধারণ ও পড়াশুনো, এই দুইয়ের ব্যয়ভার বহন করা ছিল অসম্ভব। তা সত্ত্বেও পরীক্ষার পরে চার মাস বসেছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য। কলকাতায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে জলধর নিজের কথা জানালেন। সব শুনে বিদ্যাসাগর বললেন, “এ বছরটা অন্য কলেজে ভর্তি হ, আসছে বছর তোকে সেকেন্ড ইয়ারে নেবো। মাইনে-টাইনে কিছু দিতে হবে না।” তিনি আরও বললেন, “মনে কিছু করিস না, এ বছর তোর কলেজের মাইনে আমি দেবো। তারপর সেকেন্ড ইয়ারে তো এখানেই আসছিস।” জলধরের কথায়,“আমি তখন কেঁদে ফেলেছি। মানুষের হৃদয়ে যে এত দয়া থাকতে পারে, এ আমি জানতাম না। আমার সেই অবস্থা দেখে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উঠে এসে আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ‘ওরে পাগল দারিদ্র অপরাধ নয়। আমিও তোর মতো দরিদ্র ছিলাম’।”
|
সৃষ্টি
সাময়িক পত্রপত্রিকা পরিচালন: ‘বঙ্গবাসী’, ‘বসুমতী’, ‘সন্ধ্যা’, ‘হিতবাদী’, ‘সুলভ সমাচার’, ‘ভারতবর্ষ’ ও ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’।
ভ্রমণ: প্রবাস-চিত্র, হিমালয় পথিক, হিমাচল-বক্ষে, হিমাদ্রি, দশদিন, আমার য়ুরোপ ভ্রমণ (অনুবাদ), মুসাফির মঞ্জিল, দক্ষিণাপথ, মধ্যভারত।
উপন্যাস: দুঃখিনী, বিশুদাদা, করিম সেখ, আলাল কোয়াটারমেন (অনুবাদ), অভাগী, বড়বাড়ি, হরিশ ভাণ্ডারী, ঈশানী, পাগল, চোখের জল, ষোল-আনি, সোনার বাংলা, দানপত্র, পরশপাথর, ভবিতব্য, তিনপুরুষ, উৎস, চাহার দরবেশ (উর্দু উপন্যাস, অনুবাদিত)।
গল্প: নৈবেদ্য, ছোটকাকী ও অন্যান্য গল্প, নূতন গিন্নী ও অন্যান্য গল্প, পুরাতন পঞ্জিকা (গল্প ও ভ্রমণ), আমার বর ও অন্যান্য গল্প, পরাণ মণ্ডল ও অন্যান্য গল্প, আশীর্ব্বাদ, এক পেয়ালা চা, কাঙালের ঠাকুর, মায়ের নাম, বড় মানুষ।
শিশুপাঠ্য গ্রন্থ: সীতাদেবী, কিশোর, শিব সীমন্তিনী, মায়ের পূজা, আফ্রিকায় সিংহ শিকার, রামচন্দ্র, আইসক্রিম সন্দেশ।
পাঠ্য পুস্তক বাঙলা দ্বিতীয় পাঠ, প্রথম শিক্ষা, শিশুবোধ, নবীন ইতিহাস, বঙ্গ গৌরব।
সম্পাদিত গ্রন্থ: হরিনাথ গ্রন্থাবলী, জাতীয় উচ্ছ্বাস, প্রমথনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী।
জীবনী গ্রন্থ: কাঙাল হরিনাথ
সম্মান
• ১৯১৩ তে ভারতবর্ষ পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যুক্ত হওয়ার ৯ বছর পরে ১৯২২-এর ৩ জুন ব্রিটিশ ভারতের গর্ভনর জেনারেল জলধর সেনকে ‘রায় বাহাদুর’ উপাধি দান করেন।
• ১৩৩৯-এর ১২ ভাদ্র, কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে প্রথম জলধর সংবর্দ্ধনার আয়োজন করা হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।
যে সব প্রতিষ্ঠানে আসন অলঙ্কৃত করেন জলধর সেন—
• তৃতীয় বার্ষিক মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন, ১৩২২, সভাপতি
• বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩২৯-৩০, ১৩৪৩-৪৫, সহ-সভাপতি
• সাহিত্য শাখার সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মীলন, রাধানগর ১৩৩১
• সাহিত্য শাখার সভাপতি, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, ইন্দৌর, ১৩৩৫
• সর্বাধ্যক্ষ, রবিবাসর, ১৩৩৮
• বিশিষ্ট সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪১
• নিখিলবঙ্গ জলধর সংবর্দ্ধনা, ১৩৪১
• সংবর্দ্ধনা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪২
|
|
তথ্য: পাপিয়া মিত্র
|
|
 |
|
|
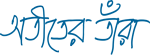

 • ছেলেবেলায় বঙ্গ বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা। হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।
• ছেলেবেলায় বঙ্গ বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা। হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। 