|
|
|
|
|
|
|
 |
পুস্তক পরিচয় ২... |
|
| রাজনীতির রূপ |
ক্ষমতাসর্বস্ব অতি-রাজনীতির সদম্ভ চেহারা, বিকল্পের চেহারা বা খানিক উন্মোচিত অন্য স্বর, আর বিকল্প সমাজবোধ গড়ে তোলার জন্যে জরুরি যে  শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চিন্তা— এ নিয়েই আলোচনা অভ্র ঘোষের অতি রাজনীতির সংকট-এ (এবং মুশায়েরা, ২৫০.০০)। ক্ষমতার দাপট থেকে হারানো মূল্যবোধ, ঐতিহ্যে মেশা এক শুশ্রূষাময় সমাজজীবনে ফিরবার চেষ্টা যেন সৌরীন ভট্টাচার্যের গাথা উপগাথা-য় (পত্রলেখা, ২২০.০০)। গণতন্ত্রের স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগরের ভাবনার জগত্, এমন বিবিধ বিষয়াদি নিয়েই এ-বই। নকশাল আন্দোলন কী ভাবে বাংলা সাহিত্যকেও আলোড়িত করেছিল, ইতিহাসচেতনায়, জীবনবোধে, এমনকী আঙ্গিকেও, তা নিয়ে ফটিকচাঁদ ঘোষের নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য (বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৩৫০.০০)। অশ্রুকুমার সিকদারের কিল মারার গোসাঁই/ কমিউনিস্ট আমলাতন্ত্র ও সাহিত্যিক-শিল্পী-মেধাজীবী-তে (দীপ, ২৫০.০০) মুক্তি বা স্বাধীনতার দিশারী শিল্পী-সাহিত্যিকদের উপর কী ভাবে নেমে এসেছিল কমিউনিস্ট আমলাতন্ত্রের শাসন-পীড়ন, তা নিয়েই। ইসলাম সম্পর্কে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধারণা বহু ক্ষেত্রেই স্পষ্ট নয়। জাহিরুল হাসান-এর মুসলমানকোষ (পূর্বা, ২০০.০০) এই অভাব পূর্ণ করার উদ্যোগ। পশ্চিম প্রান্তের দাঙ্গা নিয়ে যতখানি আলোচনা হয়েছে, পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গের দাঙ্গা সেই তুলনায় অনালোচিত। সুকুমার বিশ্বাস কমিউনাল রায়টস ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল: ১৯৪৭-১৯৬৪ (পারুল, ২৯৫.০০) বইয়ে দুই বঙ্গের দাঙ্গার ইতিহাস নথিভুক্ত করেছেন। বাংলা ভাষার অধিকার চেয়ে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ, সেই স্বাধীনতা অর্জনের পর কী ভাবে দেশটি বদলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ‘মৌলবাদী আধুনিক রাষ্ট্র’ হয়ে উঠল, তাঁর বাংলাদেশ বাঙালি মানস রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা (কৃষ্টি, ৭৫.০০) বইয়ে সেই ইতিহাস সন্ধান করেছেন মুনতাসীর মামুন। ‘ভারতবর্ষ যে সমস্ত বড়রকম সমস্যায় ভোগে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক বোধহয় শিক্ষার ঘাটতি এবং অনৈক্যের প্রাচুর্য। এই দুটি অন্তরায়ের বৈশিষ্ট এবং প্রকোপ কুমার রাণার অসাধারণ বইটিতে সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে।’— আধিপত্য ও লোকপ্রজ্ঞা (আনন্দ, ২০০.০০) বইটির মুখবন্ধে লিখেছেন অমর্ত্য সেন। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের দায়দায়িত্ব নিয়ে সামাজিক বিতর্ক ক্রমে জোরদার হয়ে উঠেছে। সেই প্রেক্ষিতেই বিজ্ঞানের দায় বিজ্ঞানীর দায়িত্ব (অবভাস, ১৫০.০০) বইটিতে জিন-গবেষক তুষার চক্রবর্তী কিছু জরুরি প্রশ্ন তুলেছেন। ১৮৯২-এর ৫ ও ৬ জুন হিন্দু কলেজে ক্লাস নিয়েছিলেন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চিন্তা— এ নিয়েই আলোচনা অভ্র ঘোষের অতি রাজনীতির সংকট-এ (এবং মুশায়েরা, ২৫০.০০)। ক্ষমতার দাপট থেকে হারানো মূল্যবোধ, ঐতিহ্যে মেশা এক শুশ্রূষাময় সমাজজীবনে ফিরবার চেষ্টা যেন সৌরীন ভট্টাচার্যের গাথা উপগাথা-য় (পত্রলেখা, ২২০.০০)। গণতন্ত্রের স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগরের ভাবনার জগত্, এমন বিবিধ বিষয়াদি নিয়েই এ-বই। নকশাল আন্দোলন কী ভাবে বাংলা সাহিত্যকেও আলোড়িত করেছিল, ইতিহাসচেতনায়, জীবনবোধে, এমনকী আঙ্গিকেও, তা নিয়ে ফটিকচাঁদ ঘোষের নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য (বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৩৫০.০০)। অশ্রুকুমার সিকদারের কিল মারার গোসাঁই/ কমিউনিস্ট আমলাতন্ত্র ও সাহিত্যিক-শিল্পী-মেধাজীবী-তে (দীপ, ২৫০.০০) মুক্তি বা স্বাধীনতার দিশারী শিল্পী-সাহিত্যিকদের উপর কী ভাবে নেমে এসেছিল কমিউনিস্ট আমলাতন্ত্রের শাসন-পীড়ন, তা নিয়েই। ইসলাম সম্পর্কে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধারণা বহু ক্ষেত্রেই স্পষ্ট নয়। জাহিরুল হাসান-এর মুসলমানকোষ (পূর্বা, ২০০.০০) এই অভাব পূর্ণ করার উদ্যোগ। পশ্চিম প্রান্তের দাঙ্গা নিয়ে যতখানি আলোচনা হয়েছে, পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গের দাঙ্গা সেই তুলনায় অনালোচিত। সুকুমার বিশ্বাস কমিউনাল রায়টস ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল: ১৯৪৭-১৯৬৪ (পারুল, ২৯৫.০০) বইয়ে দুই বঙ্গের দাঙ্গার ইতিহাস নথিভুক্ত করেছেন। বাংলা ভাষার অধিকার চেয়ে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ, সেই স্বাধীনতা অর্জনের পর কী ভাবে দেশটি বদলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ‘মৌলবাদী আধুনিক রাষ্ট্র’ হয়ে উঠল, তাঁর বাংলাদেশ বাঙালি মানস রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা (কৃষ্টি, ৭৫.০০) বইয়ে সেই ইতিহাস সন্ধান করেছেন মুনতাসীর মামুন। ‘ভারতবর্ষ যে সমস্ত বড়রকম সমস্যায় ভোগে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক বোধহয় শিক্ষার ঘাটতি এবং অনৈক্যের প্রাচুর্য। এই দুটি অন্তরায়ের বৈশিষ্ট এবং প্রকোপ কুমার রাণার অসাধারণ বইটিতে সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে।’— আধিপত্য ও লোকপ্রজ্ঞা (আনন্দ, ২০০.০০) বইটির মুখবন্ধে লিখেছেন অমর্ত্য সেন। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের দায়দায়িত্ব নিয়ে সামাজিক বিতর্ক ক্রমে জোরদার হয়ে উঠেছে। সেই প্রেক্ষিতেই বিজ্ঞানের দায় বিজ্ঞানীর দায়িত্ব (অবভাস, ১৫০.০০) বইটিতে জিন-গবেষক তুষার চক্রবর্তী কিছু জরুরি প্রশ্ন তুলেছেন। ১৮৯২-এর ৫ ও ৬ জুন হিন্দু কলেজে ক্লাস নিয়েছিলেন 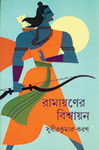 ডিরোজিয়ো, উপস্থিত ছিলেন ভিক্তর জাকমঁ।। ডিরোজিয়ো পড়িয়েছিলেন ‘ডুয়েল’ নিয়ে, তারই রোমাঞ্চকর বিবরণ শান্তিরঞ্জন বসুর ডিরোজিও’র ক্লাস-এ (বাঙলার মুখ, ১৪০.০০)। ডিরোজিও’র জীবন ও কর্ম নিয়ে টমাস এডওয়ার্ডস লেখেন হেনরি ডিরোজিও/ দ্য ইউরেশিয়ান পোয়েট, টিচার অ্যান্ড জার্নালিস্ট। বইটি ফের হাতে এল (অরুণা, ৩৯৫.০০)। মহাভারত কি মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশেরও বাচিক দলিল? ভূবিদ্যার একটি শাখার অনুসন্ধানের পদ্ধতি অনুসরণ করে মহাভারতস্থ কালক্রমিক বিবর্তনকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন দীপংকর লাহিড়ী তাঁর শাশ্বত/ মহাভারতের পুনর্পাঠ-এ (মনফকিরা, ৩০০.০০)। রামায়ণের ভিতরে যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকাশ তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা মধ্য এশিয়ায় কী ভাবে প্রসারিত হয়েছে, লিখেছেন সুধীরকুমার করণ তাঁর রামায়ণের বিশ্বায়ন-এ (আনন্দ, ২৫০.০০)। ডিরোজিয়ো, উপস্থিত ছিলেন ভিক্তর জাকমঁ।। ডিরোজিয়ো পড়িয়েছিলেন ‘ডুয়েল’ নিয়ে, তারই রোমাঞ্চকর বিবরণ শান্তিরঞ্জন বসুর ডিরোজিও’র ক্লাস-এ (বাঙলার মুখ, ১৪০.০০)। ডিরোজিও’র জীবন ও কর্ম নিয়ে টমাস এডওয়ার্ডস লেখেন হেনরি ডিরোজিও/ দ্য ইউরেশিয়ান পোয়েট, টিচার অ্যান্ড জার্নালিস্ট। বইটি ফের হাতে এল (অরুণা, ৩৯৫.০০)। মহাভারত কি মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশেরও বাচিক দলিল? ভূবিদ্যার একটি শাখার অনুসন্ধানের পদ্ধতি অনুসরণ করে মহাভারতস্থ কালক্রমিক বিবর্তনকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন দীপংকর লাহিড়ী তাঁর শাশ্বত/ মহাভারতের পুনর্পাঠ-এ (মনফকিরা, ৩০০.০০)। রামায়ণের ভিতরে যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকাশ তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা মধ্য এশিয়ায় কী ভাবে প্রসারিত হয়েছে, লিখেছেন সুধীরকুমার করণ তাঁর রামায়ণের বিশ্বায়ন-এ (আনন্দ, ২৫০.০০)। |
|
|
 |
|
|