|
|
|
|
|
|
|
 |
পুস্তক পরিচয় ১... |
|
| দেশকালের সন্ধানে দুটি চরিত্র |
| রামকুমার মুখোপাধ্যায় |
| দোজখ্নামা, রবিশংকর বল। দে’জ, ২০০.০০ |
দোজখ্নামা উপন্যাসের দু’টি প্রধান চরিত্র ফারসি-উর্দু কবি মির্জা গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯) এবং উর্দু কথাসাহিত্যিক সাদাত হাসান মান্টো (১৯১২-১৯৫৫)। ভারত ও পাকিস্তানের কবরে শুয়ে নিজেদের জীবন ও কালের কথা বিনিময় করছেন দু’জনে এমনই এক নতুন আঙ্গিকে উপন্যাসটি লেখা। এর মধ্য দিয়ে শ-আড়াই বছরের কালগত বিস্তার অর্জন করেছে লেখাটি। আখ্যায়িত হয়েছে সিপাহি বিদ্রোহ থেকে দেশভাগ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের নানা রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও আর্থ-সামাজিক সংকট-সম্ভাবনা। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে নিরাপত্তাব্যত্যয়ী এক কবি আর এক কথাকারের সমাজ তথা রাষ্ট্র-উদ্বৃত্ততার কথা এই কাহিনিতে।
গালিবের জন্ম আগরা শহরে হলেও তাঁর পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন সমরখন্দ থেকে যোদ্ধা হিসেবে। গালিব যুদ্ধবিগ্রহের ধারেকাছে ছিলেন না, যদিও খুবই সুপুরুষ ছিলেন তিনি। এই রূপের সঙ্গে বাক্পটুতার কারণে সান্ধ্য-আসরে সহজেই জয় করেন নারী-হৃদয়, যার রাগ-অনুরাগ আনন্দ-বিষাদের কথা তাঁর গজল ও শের জুড়ে। আর এমন রূপবান কাব্যপ্রাণ যুবকের যা করার কথা, তা-ই করলেন তিনি আকাশে ওড়ালেন পতংগ্ আর মাটিতে খেললেন জুয়া। আকাশে অন্যের পতংগ্ কখনও কাটলেন, কখনও নিজেই কাটা পড়লেন আর নীচের খেলায় কখনও জিতলেন, কখনও হারলেন। সবশেষে জাত খেলোয়াড় যা করে, তা-ই করলেন জীবনটাকেই বাজি ধরলেন আশমান ও জমিনের দুই খেলাতেই।
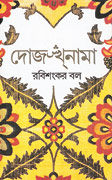 এই জীবনেরই এক পর্বে আগরা ছেড়ে দিল্লি আসা, সেখান থেকে ১৮২৭-এ কানপুর, লখনউ, কাশী হয়ে কলকাতায় পেনশনের টাকা বাড়ানোর দরবার, ব্যর্থ হয়ে আবার দিল্লি ফেরা শূন্য হাতে। এ সব কথা ধরা থাকে গালিবের শের ও গজলে, যা সুন্দর অনুবাদে স্থান পায় উপন্যাসে। চিঠিপত্রেও রয়েছে অজস্র তথ্য, কিন্তু তার সব সত্য ধরলে বিভ্রান্তি ঘটে নানা। গালিবের কাব্যে পরতে পরতে যেমন তাঁর জীবন, তেমনই তাঁর চিঠিপত্রে নানান কাল্পনিক উপাদান এ এক আজব খেলা। গালিবের কাশীবাসের পর্বটি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেন রবিশংকর তাঁর উপন্যাসে। মণিকর্ণিকার ঘাট, গঙ্গার হাওয়া, চিতার আগুন, অভিজাত গণিকা এবং কবীরদাসের ‘চরখা চলৈ সুরত-বিরহিনকা’ গীতের সুরে এই প্রাচীন নগরটি যেন একই সঙ্গে বাস্তব ও অপার্থিব। পরের অংশ কলকাতা। রবিশংকর শুনিয়েছেন কলকাতার সবুজ শ্যামলিমা, গঙ্গার বাতাস, সুন্দরী নারী, শরাব এবং আম কতখানি আলোড়িত করেছিল গালিবকে। কিন্তু নিধুবাবুর ‘সায়েবদের মতো এই শহরেরও হৃদয় নেই’, এর বিস্তারে যাননি। গেলে হয়তো অন্য মাত্রা পেত এই অংশটি। এই জীবনেরই এক পর্বে আগরা ছেড়ে দিল্লি আসা, সেখান থেকে ১৮২৭-এ কানপুর, লখনউ, কাশী হয়ে কলকাতায় পেনশনের টাকা বাড়ানোর দরবার, ব্যর্থ হয়ে আবার দিল্লি ফেরা শূন্য হাতে। এ সব কথা ধরা থাকে গালিবের শের ও গজলে, যা সুন্দর অনুবাদে স্থান পায় উপন্যাসে। চিঠিপত্রেও রয়েছে অজস্র তথ্য, কিন্তু তার সব সত্য ধরলে বিভ্রান্তি ঘটে নানা। গালিবের কাব্যে পরতে পরতে যেমন তাঁর জীবন, তেমনই তাঁর চিঠিপত্রে নানান কাল্পনিক উপাদান এ এক আজব খেলা। গালিবের কাশীবাসের পর্বটি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেন রবিশংকর তাঁর উপন্যাসে। মণিকর্ণিকার ঘাট, গঙ্গার হাওয়া, চিতার আগুন, অভিজাত গণিকা এবং কবীরদাসের ‘চরখা চলৈ সুরত-বিরহিনকা’ গীতের সুরে এই প্রাচীন নগরটি যেন একই সঙ্গে বাস্তব ও অপার্থিব। পরের অংশ কলকাতা। রবিশংকর শুনিয়েছেন কলকাতার সবুজ শ্যামলিমা, গঙ্গার বাতাস, সুন্দরী নারী, শরাব এবং আম কতখানি আলোড়িত করেছিল গালিবকে। কিন্তু নিধুবাবুর ‘সায়েবদের মতো এই শহরেরও হৃদয় নেই’, এর বিস্তারে যাননি। গেলে হয়তো অন্য মাত্রা পেত এই অংশটি।
গালিবের দিল্লি ফেরার পর পাওনাদারদের তাগিদা, জুয়ায় ধরা পড়ে গ্রেফতার, পারিবারিক দুর্যোগ, সিপাহি বিদ্রোহ পর্ব, মুশায়েরাতে বারে বারে অপমানিত হওয়া থেকে যে বাকি কাহিনি রবিশংকর লেখেন, তার ভেতর এক দিকে কাজ করেছে তাঁর শ্রম, অন্য দিকে তাঁর উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক কল্পনা। গালিব-কাহিনিতে র্যাঁবো, জীবনানন্দ, শঙ্খ ঘোষ থেকে এই সময়ের বেশ কিছু কবির কবিতা ব্যবহারও আকর্ষণীয়, কিন্তু যেখানে র্যাঁবোর ‘আই অ্যাম দি আদার’ দিয়ে গালিবকে সূত্রায়িত করতে চান, তা যেন কিছুটা সরলীকরণ মনে হয়। আরও গভীর এক জীবনদর্শন থেকে তৈরি হয়েছে গালিবের কাব্যচিন্তা, যার জন্ম পারস্যে। দর্শন, অতীন্দ্রিয়বাদ, নান্দনিকতা এবং গৌণতার রসায়নে গালিবের যে কাব্য-ভাবনা, তা একই সঙ্গে আত্মপ্রক্ষেপ ও আত্ম-আবিষ্কার। সেই একক সার্বভৌম যাত্রায় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবই তুচ্ছ হয়ে যায়।
উপন্যাসের দ্বিতীয় যে মুখ্য চরিত্র মান্টো, সে-জীবনও এক বৈশাখী ঝড়। জন্ম বিত্তশালী পরিবারে, যেখানে সোনা-রুপোর ‘বাটখারা’ (কাশ্মীরি শব্দ ‘মিন্ট’, যা ‘মান্টো’ পদবির উৎস) দিয়ে ওজন করা হত। কিন্তু কৈশোরে পৌঁছে সম্পদে মন বসেনি মান্টোর, কখনও ঘুরছেন অমৃতসরে পির-দরবেশদের সমাধিক্ষেত্রে, কখনও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছেন জালিয়ানওয়ালাবাগের গাছের নীচে বসে, কখনও স্কুলগামী কিশোরীদের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন কাকে প্রেম নিবেদন করবেন। শুনছেন রাগসংগীত, পড়ছেন অজস্র বই, চেষ্টা করছেন কবিতা লেখার আর নানা নেশায় মজে আছেন। মান্টোর এই উদ্দাম পর্বটি এক সংবেদী গদ্যে তুলে ধরেছেন রবিশংকর। এই সময়ে আজিজের হোটেলে পরিচয় ঘটে সাংবাদিক আবদুল বারি আলিগের সঙ্গে, যিনি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী উপন্যাস, গল্প, নাটকের প্রতি কিশোরটিকে অনুরক্ত করে তোলেন। অনুবাদে হাত দেন মান্টো, পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা সম্পাদনা করেন। বেনামে গল্পও লেখেন ‘তামাশা’ নামে। ১৯৩৪-এ ঢুকলেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তেন মাঝেমধ্যেই। দিদির কাছে অর্থ সাহায্য নিয়ে মান্টো কাশ্মীরের বাতোতে মাস তিনেক কাটান। এখানেই প্রেমে পড়েন বেগু নামের একটি মেয়ের, যে ছাগল চরাত পাহাড়ের কোলে। মান্টোর প্রথম প্রেমের মানস-দৈহিক অনুভূতি জরুরি তির্যকতায় জায়গা পেয়েছে উপন্যাসে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই বেগুর স্মৃতি বেশ স্পষ্ট মান্টোর কয়েকটি গল্পে।
পিতৃবিয়োগের পর অর্থনৈতিক চাপে মান্টো সন্ধান করেন চাকুরির এবং পেয়েও যান লাহৌরে, কিন্তু এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন জনপ্রিয় সাংবাদিকতায়। সেখানে হিরামান্ডির যৌনপল্লিতে তিনি পরিচিত হন নগ্ন ও রূঢ় এক বাস্তবতার সঙ্গে, যা তাঁর গল্পে স্থায়ী ছাপ ফেলে। ১৯৩৬-এর দিকে ফেরেন বম্বেতে, চলচ্চিত্র পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে। চলচ্চিত্রের সংলাপও লিখতে থাকেন, কিন্তু অচিরেই বোঝেন তাঁর লেখক সত্তা এতে কোনও ভাবেই রূপ পাচ্ছে না। অন্য দিকে প্রগতিশীল লেখক-আন্দোলন তখন আবেগ ও সৃষ্টিতে আন্দোলিত হচ্ছে। মান্টোর সেই যন্ত্রণা, শূন্যতার কথা আছে এই উপন্যাসে ‘গাড়ির পেছনে যে পাঁচ নম্বর চাকাটা আটকানো থাকে, কাজে লাগতে পারে, না-ও পারে, আমি সেই চাকাটা’। ওই পর্বে আরব গোলির একটি অন্ধকার খোলিতে মান্টো ‘দুমড়ে-মুচড়ে’ জীবন কাটান, রবিশংকর যাকে বলেছেন ‘দোজখ্’। সেখানে তখন যৌনকর্মী, দালাল, মালিশওয়ালা, পানওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা, ছুরি-পিস্তলবাজদের বাস। তারপর বিবিজান ও দিদির উদ্যোগে কাশ্মীরি মেয়ে শফিয়ার সঙ্গে নিকাহ হয়ে গেল ১৯৩৯-এর এপ্রিলে। বছরখানেক শফিয়া চাচার বাড়িতে থাকার পরে মান্টো একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সংসার পাতেন এবং ওই সময়েই তাদের একটা সন্তান হয়, যার নাম রাখলেন ‘আরিফ’।
বম্বের কাজটি আবার হারালেন এবং অচিরেই দিল্লির আকাশবাণীতে নিযুক্ত হলেন, যেখানে তখন কৃষণ চন্দর, এন এম রসিদ, রাজিন্দর সিংহ বেদির মতো লেখক কর্মরত। মান্টো দিল্লি চললেন ঠিকই, কিন্তু বম্বের ‘দোজখের’ অভিজ্ঞতাই তাঁর সৃষ্টির অগ্রাধিকারগুলিকে নির্দিষ্ট করে দিল নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান থেকে নিরঙ্কুশ বাস্তবতাকে সপ্রতিভতায় তুলে ধরা। দেড় বছরের দিল্লিবাসও সৃষ্টির দিক দিয়ে বেশ ফলপ্রসূ হয়েছিল। কিন্তু ছেলে আরিফের মৃত্যুতে বিষাদ-বিমূঢ় হলেন এবং এক সময় দিল্লি ছেড়ে বম্বে ফিরে গেলেন তাঁর একটি বেতার নাটকের পরিবর্তনকে মেনে নিতে না পেরে। ওই পর্বে তাঁর সংঘাতও চলেছিল প্রগতিবাদী ও প্রাচীনপন্থী দু’পক্ষের সঙ্গেই। ১৯৪৫-এর শীতে অসমত চুগতাইয়ের সঙ্গে লাহৌরে যান কোর্টে অশ্লীলতার জবাবদিহি করতে। মান্টো আর ইসমতের পারস্পরিক ভালবাসার একটা ফল্গু স্রোত প্রবাহিত হয়েছে সারা উপন্যাস জুড়েই।
বম্বেতে ভালই কাটছিল মান্টোর জীবন নতুন নতুন গল্প ও স্ক্রিপ্ট লিখে, কিন্তু ১৯৪৭-এ তাঁর গল্পের পরিবর্তে যখন চুগতাইয়ের গল্প নেওয়া হল একটি চলচ্চিত্রে, মান্টো আবার আত্মাভিমানী হয়ে উঠলেন। সঙ্গে দাঙ্গা এবং তীব্র ধর্মান্ধতায় চূড়ান্ত মর্মাহত হলেন। এমন এক অনির্দিষ্টতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খানিকটা পারিবারিক চাপে সপরিবারে পাকিস্তানযাত্রা। তার পরের আট বছর জুড়ে জীবিকাগত অনিশ্চয়তা, অশ্লীলতার নানান অভিযোগ, সৃষ্টিশীলতার পরিবেশের অভাব, মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান এবং দু-দু’বার মানসিক হাসপাতালে ভর্তি। আর এরই মধ্যে আলোড়িত করার মতো একের পর এক গল্প লেখেন মান্টো, মৃত্যুর দিকে পা ফেলতে ফেলতে। এই পর্বের বিপদ, যন্ত্রণা, রাগের অনুভূতি নাটকীয়তা ও পরাদৃষ্টিময়তার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন কথাকার।
নিজস্ব গদ্যে, বিবরণের একমাত্রিকতাকে নানা ভাবে ভেঙে, দোজখ্নামা-কে একটি আধুনিক উপন্যাস হিসেবে গড়ে তুলেছেন রবিশংকর। তবে, মান্টো তাঁর জীবনকে গাড়ির যে পঞ্চম চাকার উপমায় উল্লেখ করেন যা ঘোষিত ভাবেই তিনি নেন তুর্গেনিভ থেকে তা বহু ব্যবহারে ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। উপন্যাসের কয়েক জায়গায় ‘ভারতবর্ষ’ থেকে যেন ‘হিন্দুস্তান্’ শব্দটি যেন বেশি উপযুক্ত হত যেমন দরবেশের গল্পে, ‘এক সওদাগর ব্যবসার কাজে ভারতবর্ষে যাবে’। আর ‘তরমুজের মতো একফালি বারান্দা’-ও বোধহয় সংশোধিত হওয়া দরকার। |
|
|
 |
|
|