|
|
|
|
| |
| সম্পাদক সমীপেষু... |
| দেশভাগ এড়ানোর সুযোগ ‘ভেস্তে গেল’? |
| উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা (‘সর্দার পটেল: ইতিহাস এত সরল নয়’, ৬-১১) পড়ে মনে হয়, নেহরু এবং পটেল হরিহর-আত্মা ছিলেন, এবং সে কথা মোদী গোপন করে রেখেছেন। অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের বই থেকে মাউন্টব্যাটেনের উক্তি উদ্ধৃত করে উদয়নবাবু হয়তো এ-ও বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিয়ে যে গোল বেধেছে তার প্রণেতাও পটেলই। কিন্তু এখানে নেহরুর কিছু কীর্তি মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। তিনি একটি বাক্যে সেরে দিয়েছেন, “অনতিঅতীতে ক্যাবিনেট মিশন প্রকল্প প্রায় সম্পূর্ণই ভেস্তে গেছে”। কিন্তু ভেস্তে দিল কে? আর কেউ নন, জওহরলাল নেহরু। এবং এই ইতিহাসটি লিপিবদ্ধ করে গেছেন আর এস এস-এর কোনও ঐতিহাসিক নয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। তাঁর আত্মজীবনী ‘ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে। কিন্তু এতে একটি শর্ত ছিল যে, এর তিরিশটি পাতা তখন প্রকাশ হবে না, হবে তিরিশ বছর পরে। এবং ১৯৮৭ সালে যখন এই ইতিহাস প্রকাশিত হল, তখন তাতে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য ছিল, তা হল এই: ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন এসে ‘গ্রুপিং প্ল্যান’ নামে ভারতকে অখণ্ড রাখার একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করে, যাকে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ দুই-ই মেনে নিয়েছিল। |
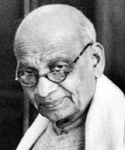 |
কিন্তু ১০ জুলাই ১৯৪৬ সালে বোম্বাইতে (অধুনা মুম্বই) কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি জওহরলাল কংগ্রেসের আর কারও সঙ্গে আলোচনা না-করে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন এবং তাতে বলেন যে, কংগ্রেস যখন ব্যবস্থাপক সভায় বসবে, তখন তারা কোনও রকম পূর্বশর্ত মানবে না। গ্রুপিং প্ল্যানে সম্মতি দিয়ে জিন্না একটু বেকায়দায় ছিলেন। তিনি নেহরুর এই উক্তিকে লুফে নেন এবং ঘোষণা করেন যে, এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা গ্রুপিং প্ল্যানের প্রতি সম্মতি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। এবং ১৬ অগস্ট ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’-এর (ডিরেক্ট অ্যাকশন) ডাক দিচ্ছেন। সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কলকাতায় নরমেধ যজ্ঞের চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, যাতে আনুমানিক কুড়ি হাজার মানুষের প্রাণ যায়। এই হল ‘ভেস্তে যাওয়া’র ইতিহাস। এটা ভেস্তে না-গেলে দেশভাগ হত না। এবং আরও কয়েক কোটি নরনারীর প্রাণ, মান, ইজ্জত, সম্পত্তি সম্ভবত যেত না।
মৌলানা আজাদ অত্যন্ত খেদের সঙ্গে বলেছেন, এটা হল সেই রকম একটা ঘটনা, যা ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেয়। আরও বলেছেন, উনি যদি কংগ্রেসের সভাপতি পদ ছাড়ার সময় নেহরুর নাম প্রস্তাব না-করে পটেলের নাম প্রস্তাব করতেন, এবং পটেল সভাপতি হতেন, তা হলে তিনি কখনও এবংবিধ ভুল করতেন না।
অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন মাউন্টব্যাটেনের যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, এবং যার উপরে উদয়নবাবু নির্ভর করেছেন, তা পটেলের স্বভাবের সঙ্গে এতই সঙ্গতিহীন যে, মাউন্টব্যাটেনের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উদ্রেক করে।
আর একটি কথা। কাশ্মীর নিয়ে এক কলম ধরে উদয়নবাবু আলোচনা করলেন। কিন্তু তার মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়য়ের নাম এক বারও উল্লেখ করলেন না!
তথাগত রায়। কলকাতা-৯১
|
| কী ভাবে জল ভরা যায় |
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মাটির নীচের জলস্তর নিয়ে কিছু দিন আগে সংবাদ প্রতিবেদন পড়েছিলাম ‘জলেই গেল বৃষ্টির জল, পাতাল-পিপাসা না-মিটিয়ে সাগর প্রাপ্তি’ (২১-৮)। সম্প্রতি পড়লাম দেবদূত ঘোষ ঠাকুরের নিবন্ধ ‘জল ধরলেই জল ভরা যায় না’ (২৭-১০)। কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলস্তর অনেক নীচে, আর বৃষ্টি হলেও সেখানে জল পৌঁছয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূ-জল পর্ষদের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্তার মন্তব্য, ‘মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি ও বর্ধমানের কিছু এলাকায় পুকুর খুঁড়ে বা সংস্কার করে মাটির খুব কাছাকাছি বালিমাটির স্তর থাকায় পুকুরের জল সহজেই সেই স্তর ভেদ করে চলে যায় মাটির নীচের মূল জলস্তরে। কিন্তু কলকাতার কাছাকাছি এলাকায় পুকুরের নীচেই রয়েছে ১৮ থেকে ২০ ফুট কাদামাটির স্তর, যা বৃষ্টির জল নীচে নামার প্রতিবন্ধক।’ জলবিজ্ঞানীরা বলছেন, কলকাতায় যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তার শতকরা নব্বই ভাগ গড়িয়ে চলে যায় সমুদ্রে, মাটির নীচে জলের স্তরে পৌঁছতেই পারে না। ওই জলের স্তরটা রয়েছে, এলাকা ভেদে, ৮০ থেকে ২৫০ মিটার নীচে। বৃষ্টির জলকে পাঠিয়ে দিতে হবে সেই স্তরে। কী করে বৃষ্টির জল মাটির নীচের জলস্তরে পাঠানো যায়?
তাই আমি এক বিশেষ ধরনের কূপ তৈরি করার পরামর্শ দিতে পারি। এর গভীরতা হবে ১০০/১৫০ ফুট, প্রয়োজনে ৩০০/৩৫০ ফুট, ব্যাস আড়াই ফুট। তার পাশে একটি ‘ক্যাচ-পিট’ থাকবে। জলভাসি নোংরা প্লাস্টিক ও ভাসমান আবর্জনা ওর মধ্যেই জমা হয়ে থাকবে। শুধু বিশুদ্ধ বৃষ্টির জল একটি সাইফন মারফত গভীর কূপের মধ্যে জমা হবে। যার গায়ে কিছু ফুটো থাকবে, যাতে সহজেই বৃষ্টির জল পার্শ্ববর্তী ভূগর্ভে সঞ্চারিত হয়। ঠিক ম্যানহোলের ঢাকনার মতো উপরিভাগ ঢাকা থাকবে। যদি কখনও প্রচুর জমা জল ঢাকনা খুলে প্রবেশ করাতে হয়, সে ক্ষেত্রে, জমে থাকা ভাসমান বর্জ্য তোলার সুবিধার্থে দুটি পোক্ত লোহা বা কংক্রিটের জালি বসানো যেতে পারে— একটি ১ ফুট নীচে, অন্য একটি আরও ৬ ফুট নীচে। সবচেয়ে ভাল, পার্কের মধ্যেই বা রাস্তার ফুটপাতে বৃষ্টি-জলভাসি এলাকায় বিভিন্ন দূরত্বে এই রকমের গভীর কূপ বসানো যেতে পারে।
প্রসঙ্গত, গালিপিট, ম্যানহোলে মানুষ না নামিয়ে সহজে কাদা-মাটি তোলার জন্য একটি হাতিয়ার উদ্ভাবন করেছি: ‘গ্রাবিং বাকেট’, যা ন্যাশনাল ইনোভেশন কাউন্সিল থেকে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ প্রশংসিত ও পুরস্কৃত করেন। ওই যন্ত্র দ্বারা সহজেই কিছু কূপ খনন করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ‘জল ধরো, জল ভরো’ আন্দোলনের সার্থক রূপায়ণ হবে।
জিতেন্দ্রনাথ দাস। প্রাক্তন সহকারী বাস্তুকার (সিভিল), কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
|
| শুধু তিস্তা নয়, মুক্তি চাই করলারও |
| দেবেশ রায় (‘মুখ্যমন্ত্রী ভগীরথের কাজ করুন’, ১-১১) লিখেছেন, ‘... একটা নদীকে নদীতে ফিরিয়ে দিলে ভগীরথতুল্য পুণ্য অর্জিত হয়।’ জলপাইগুড়ির আর এক নদী করলার সম্পর্কেও কথাটি খাটে। জলপাইগুড়ি দু’দুটি নদী দ্বারা সমৃদ্ধ। ছোট্ট শহরটির একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তা আর মাঝখান দিয়ে করলা। দুর্ভাগ্য এই যে, নদী হওয়া সত্ত্বেও ‘বয়ে চলেছে’ কথাটা করলা সম্বন্ধে বলা চলে না। কেননা, কাণ্ডজ্ঞানহীন, নির্দয় মানুষ করলার তিস্তামুখী দিকটা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে, করলা হয়ে উঠেছে শহরের সমগ্র জঞ্জালের ভাণ্ডার। কোথায় নদীটি শহরের শোভাবর্ধন করে এর আবহাওয়া মনোরম করে তুলবে, তার পরিবর্তে নদীর দূষিত জল, পচা আবর্জনা মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করে চলেছে। |
 |
করলার আটকে দেওয়া দিকটা মুক্ত করে বহমান থাকতে দিলে নদীটির প্রতি এতদিনকার হৃদয়হীন অত্যাচারের খানিক পরিশোধ হবে, শহরের সৌন্দর্যায়নও বৃদ্ধি পাবে। জলপাইগুড়ি ও সন্নিহিত ডুয়ার্স অঞ্চলে পর্যটক আকর্ষণের বিরাট সম্ভাবনা অব্যবহৃত রয়েছে। করলাকে প্রবহমান করে নৌকাযোগে প্রমোদ-বিহারের আয়োজন করে জলপাইগুড়িকে করে তোলা যায় গরুমারা, জলদাপাড়া প্রভৃতি অরণ্যে ভ্রমণের কেন্দ্রস্থল। নভেম্বর-ডিসেম্বরে তিস্তার তীর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন হতে পারে বাড়তি আকর্ষণ।
সঞ্জিত ঘটক। কলকাতা-১০৩ |
|
|
 |
|
|