|
|
|
|
|
|
|
|
| সুমনামি |
কবীর সুমন
|
সরোদ
শিল্পী প্রত্যুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মার্গসংগীতের শিল্পী প্রত্যুষ স্টুডিয়োশিল্পী হিসেবেও দক্ষ ও নামজাদা। আমার বিভিন্ন রেকর্ডিং-এ বাজিয়েছেন রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গেও। সপ্তকের সব ক’টি স্বর শুদ্ধ হলে তার শুদ্ধ গান্ধারকে ষড়জ মেনে বাকি স্বরগুলি গাইলে বা বাজালে ভৈরবী রাগটি ধরা দেয় প্রত্যুষ একমত। সেই হিসেবে, রবীন্দ্রনাথের ‘ও যে মানে না মানা’ গানটি, ধরা যাক বি-ফ্ল্যাট স্কেলে গাইলে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলতে গেলে ন্যাস স্বরটি হয় ডি। ‘মানা’, ‘না’—স্থায়ীর দুটি লাইনই শেষ হচ্ছে ডি পরদায়, অর্থাৎ বি-ফ্ল্যাটের পরদাটিকে ষড়জ মানলে শুদ্ধ গান্ধারে। অন্তরার দ্বিতীয় লাইনটিও শেষ হচ্ছে ওই পরদাতেই। রচনার ধরন থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, শুদ্ধ গান্ধারই অভিমুখ। আমরা মোকাম বলতে পারি। ফলে এটিকে লুকনো ভৈরবীর প্রথম স্বর ষড়জ বা ‘সা’ বলা যায়। এটুকু মাথায় রেখে গানটি গাইলে আমরা ভেতরে ভেতরে ভৈরবীর আমেজ পাব, যদিও আমাদের মূল পরদা বি-ফ্ল্যাটের নিরিখে স্বরগুলি আপেক্ষিক ভাবে শুদ্ধ। আমার মতে স্বরের এই আপেক্ষিকতার খেলাটি রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ অবদান।
প্রত্যুষ আমার বিশ্লেষণ শুনলেন এবং মনে করিয়ে দিলেন যে ‘ও যে মানে না মানা’-র স্বরলিপিতে কিন্তু ভৈরবীর স্বরগুলিই আছে। অর্থাৎ, স্বরলিপি অনুযায়ী ওই গানটি ভৈরবীতেই বাঁধা। এই হল আমাদের দেশের এক সনাতন সমস্যা। আধুনিক বাংলার যে গীতিকার-সুরকারদের নাম শুনলেই আমরা গড় করি, তাঁরা বেঁচে ছিলেন অনেক বছর আগে। তাঁদের সময়ে হয়তো এ রকম একটা রীতি ছিল যে, গান যদি বাঁধতেই হয় তা হলে কোনও-না-কোনও রাগের ভিত্তি লাগবেই। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ রাগাশ্রয়ী গান বাঁধলেও রাগানুগত্য কিন্তু দেখাননি। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ, শুনেছি লিখেছিলেন: ‘আমার আধুনিক গানে রাগ তালের উল্লেখ নেই বলে আক্ষেপ করেছিস’। |
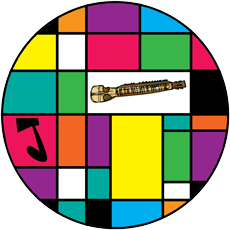 |
| ছবি: সুমন চৌধুরী |
এই একটি কথার মধ্য দিয়ে একাধিক জিনিস বেরিয়ে আসে:
১) গান বাঁধলে রাগ ও তাল জানিয়ে দেওয়ার যে রীতি রবীন্দ্রনাথের আমলে তখনও ছিল, তিনি আর তা মানলেন না।
২) তাঁর গান ‘আধুনিক গান’।
৩) পুরনো দস্তুর তিনি না মানলেও তা মানার মতো মানুষ তাঁর কাছাকাছিই ছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের স্বরলিপি নিজে করতেন না, করতেন অন্যরা। নতুন কোনও গান তাঁর কাছ থেকে তুলে নিয়ে কেউ স্বরলিপি করে ফেলতেন। তার পর সেই স্বরলিপি তিনি কী ভাবে যাচাই করে নিতেন, সে বিষয়ে আমি অন্তত কিছু জানি না। এ বিষয়ে কোনও লেখা আমি পড়িনি। তেমনই, রবীন্দ্রনাথ কি শুধুই একা একা বসে খালি গলায় সুর বানাতেন, না কোনও কোনও গানে তাঁর সঙ্গে কেউ ধরা যাক, পিয়ানোয় সংগত করতেন সে সম্পর্কে কোনও আলোচনা আমি পড়িনি, শুনিওনি। ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি, রবীন্দ্রনাথের গান বললেই শিক্ষিত, বয়স্ক বাঙালি এসরাজ যন্ত্রটির কথাই ভাবেন ও বলেন বেশি। এই যন্ত্রে মিড়ের কাজ ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথের গানে যথেষ্ট মিড়। কেন জানি না, পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশক পর্যন্ত তো বটেই, এমনকী তার পরেও খেয়াল করেছি কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের গান গাইলেই মিড়গুলিকে যেন আরও মিড়িয়ে দেন। ‘ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগো উতলা হাওয়া’ গানটি কেউ কেউ ধরলেই ‘ধী’ থেকে ‘রে’ পর্যন্ত যেতে অনেকটা সময় নিতেন। বেশির ভাগ গানেই লয় হত ঢিমের দিকে। ‘আমরা নূতন যৌবনেরই দূত’ গাইতে গিয়েও অনেক শিক্ষিত বাঙালি পারলে ‘আছে দুঃখ আছে মৃত্যু’র লয়টাই ধরতেন। এই ধরনের ঢিমে, মিড়সর্বস্ব গায়কির সঙ্গে আমাদের পরিচিত মরে-যাই-মরে-যাই ঢঙে বাজানো এসরাজ ভালই যায়। মিড়প্রধান রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে কাঁদো-কাঁদো এসরাজ শুনে শুনে আমাদের অবস্থা এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, এই যন্ত্রটি যে কতটা ক্ষমতা রাখে, তা আমরা ভেবেও দেখিনি, রণধীর রায় নামে এক আশ্চর্য শিল্পীকে পাওয়ার আগে। এসরাজকে তিনি সংগীতের অন্য এক স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। যন্ত্রটিকে পালটেও নিয়েছিলেন তিনি নিজের প্রয়োজন মতো। রণধীর রায়। বিস্ময়কর মুনশিয়ানা ও সৃষ্টিশীলতার অধিকারী এই শিল্পীকে এ দেশে ক’জন মনে রেখেছেন? তেমনি, এসরাজের ব্রিজে দম-ঘোরানো গ্রামোফোনের ধ্বনি-প্রক্ষেপণ যন্ত্রাংশটি জুড়ে দিয়ে যে পান্নালাল ঘোষ তারসানাই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁকেই বা মনে রেখেছেন ক’জন এই দেশে?
এক দল রবীন্দ্রসংগীতবিশারদ ও পরম বোদ্ধা আবার দীর্ঘ কাল ধরে গম্ভীর মুখে বলে এলেন যে, রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে একমাত্র তানপুরা চলে, আর কিছু না। হারমোনিয়াম বাজালে আঁতকে উঠতেন এঁরা। ইদানীং সংগীতের অনেক অবনতি হয়তো হয়েছে, কিন্তু একটা লাভ হয়েছে: এসরাজ-সর্বস্বতার মতো তানপুরা-সর্বস্বতার প্রবক্তারা ক্রমশ লোপ পেয়েছেন। মজার কথা হল, ধরুন যদি রবীন্দ্রনাথের ‘সকলই ফুরালো’ গানটি শুধু তানপুরা ছেড়ে গান তো অন্তরায় বিপাকে পড়ে যাবেন। কারণ, অন্তরায় রবীন্দ্রনাথ খরজ-পরিবর্তন করেছেন। ফলে যে পরদায়, যে ভাবে (ধরা যাক সুর-পঞ্চম) তানপুরাটি বাঁধা হয়েছিল, স্থায়ী পেরিয়ে অন্তরায় এলেই তা যাবে গুলিয়ে। কানে খুবই বেখাপ্পা লাগবে, অবশ্য ‘কান’ যদি থাকে। রবীন্দ্রনাথ এই গানটি বাঁধতে গিয়ে পাশ্চাত্য সংগীত-পদ্ধতির একটি সূত্রকে প্রয়োগ করেছিলেন। একই ভাবে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর ‘মলয় আসিয়া কয়ে গেছে’ গানটিতে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে খরজ পরিবর্তন করেছিলেন অন্তরায়। তা হলে এই গানের সঙ্গেও শুধু তানপুরা বাজলে রসভঙ্গ হওয়ার কথা।
রবীন্দ্রনাথের ‘সকলই ফুরালো স্বপনপ্রায়!’ এবং আরও বেশ কিছু গানের সুর-তাল-ছন্দ বলে দেয় যে পিয়ানো যন্ত্রটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথের গান সত্যিই আমাদের সব রকম জীবনের অঙ্গ, কিন্তু সংগীতের নানান ধারা আর বাজনার সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ছিল, তাঁর জীবনে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ভূমিকা কী ছিল, তা নিয়ে তিনি নিজেও বিশেষ বলেননি, তাঁর আশেপাশে যাঁরা ছিলেন এবং সারা ক্ষণ গুর্দেব-গুর্দেব করতেন, তাঁরাও সবিস্তারে কিছু বলেননি। রবীন্দ্রনাথের সুরগুলি শুনলে মনে হওয়ার কথা: পিয়ানোর ভূমিকা তাঁর সংগীতবোধে ভাল মতোই ছিল। কবিতা নয়, কাহিনি নয়, প্রবন্ধ নয়, ছবি নয়, গান-ই যাঁর ‘শেষ পারানির কড়ি’, সেই মানুষটির বিস্তারিত কোনও সাক্ষাৎকার নেননি কেউ তাঁর জীবনে সংগীত বিষয়ে।
যে পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথ ‘ও যে মানে না মানা’, ‘মধু-গন্ধে ভরা’ ও ‘আমি চঞ্চল হে’ সুর করেছেন, তা খতিয়ে দেখলে মনে হয় ভৈরবী রাগটিকে তিনি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। ভৈরবীতে রবীন্দ্রনাথ অনেক গান বেঁধেছেন। ধরা যাক, ‘আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও’ গানটিতে ভৈরবী যে ভাবে নিজেকে প্রকাশ করছে, ‘ও যে মানে না মানা’-তে কিন্তু সে ভাবে করছে না। বিখ্যাত ভৈরবীর বন্দিশ ‘ভবানী দয়ানী’ অনুসরণে অতুলপ্রসাদ সেনের ‘কে ডাকে আমারে’, কাজী নজরুল ইসলামের ‘যাও তুমি ফিরে’ বা সুধীরলাল চক্রবর্তীর ‘মধুর আমার মায়ের হাসি’র ভৈরবী আর ‘ও যে মানে না মানা’র ভৈরবী এক নয়। প্রথম তিনটি গানে ভৈরবী নিজেকে কোনও মতেই আড়ালে রাখতে চাইছে না। রবীন্দ্রনাথের গানটিতে কিন্তু চাইছে। কোনও রাগকে নিজের দেহে ধারণ করেও যে-গান একটু হলেও আড়ালে রাখতে চায়, সে সংগীতসৃষ্টির এক টুকরো রহস্যকে রেখে যায় ভাবী কালের জন্য। |
|
|
 |
|
|