|
|
|
|
|
|
|
 |
পুস্তক পরিচয় ২... |
|
| দুঃসাহসিক বিশ্লেষণের অভাব নেই |
| বারিদবরণ ঘোষ |
মহামানবের সাগরতীরে/ অন দ্য সিশোর অব হিউম্যানিটি, রবীন্দ্র জন্মসার্ধশতবর্ষ স্মারক-সংকলন,
মুখ্য সম্পাদক সুরঞ্জন দাস, নির্বাহী সম্পাদক বিশ্বনাথ রায়, চিন্ময় গুহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫০০.০০ |
পূর্ব-প্রচারিত রচনা অথবা নতুন লেখার সংকলন করে মনীষীদের স্মারকগ্রন্থ প্রকাশে রুচিমান বাঙালির তৎপরতা এখন লক্ষণীয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত গোল্ডেন বুক অব টেগোর, অমল হোম সম্পাদিত ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-এর রবীন্দ্র সংখ্যা অথবা পুলিনবিহারী সেন-সম্পাদিত রবীন্দ্রায়ন খণ্ডদ্বয়ের ঐতিহ্য স্মরণ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের সার্ধশততম জন্মবর্ষে আন্তর্জাতিক পাঠককে পৌঁছে দিয়েছেন ‘মহামানবের সাগরতীরে’।
ভাষাগত ভাবে গ্রন্থটি দু’টি ভাগে বিন্যস্ত— ইংরেজি এবং বাংলা রচনাসম্ভারে। আবার অনুক্রম বিচারেও দু’টি ভাগ— প্রথম ভাগের স্মরণলক্ষ্য কবির সার্ধশতজন্মবর্ষ এবং দ্বিতীয় ভাগে কবির শতবর্ষে প্রকাশিত একতা গ্রন্থটির সংযোগে রবীন্দ্র চর্চায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবনাকে যূথবদ্ধ করে তোলা হয়েছে। একতা-র ভাষাসম্পদ প্রাদেশিক অর্থে প্রথম ভাগের চেয়েও সমৃদ্ধ— বাংলা-ইংরেজির সঙ্গে এখানে মুদ্রিত হয়েছিল হিন্দি ও উর্দু রচনাও। প্রথম অংশের ভাষা বাংলা এবং ইংরেজি হলেও এর মধ্যে ভাবনার জগৎটি শ্রীলঙ্কা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, স্পেন এবং জার্মান পণ্ডিতদের বিশিষ্ট রবীন্দ্রভাবনায় সম্পুটিত হয়ে এই মহামানবকে সপ্ত মহাসাগরবর্তী করে তুলেছে এবং এখানেই বিশ্ববিদ্যালয় অভিধাটির দ্যোতনাও স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে।
প্রথম অংশে মুদ্রিত রচনার সংখ্যা পঁচিশ— এর মধ্যে বাংলা রচনা আটটি। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ বাঙালি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার। কিন্তু বাঙালি রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার প্রবীণতম বিশ্ববিদ্যালয়— দুয়েরই অভিমুখ বিশ্বের দিকে। স্বভাবতই ভাষাগত সংখ্যায় এর মূল্য স্থির হয় না। মুখ্য এবং নির্বাহী সম্পাদকগণ এর অমূল্যতা নির্ধারণ করেছেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ কবি ও শিক্ষাবিদ জো উইন্টার রচিত একটি কবিতা আদিতেই মুদ্রিত করে— ‘স্টর্ম অব স্টারস’— তারকা-বাত্যার এই প্রবাহ সমস্ত গ্রন্থটিকে পরিব্যাপ্ত, আলোড়িত এবং আলোকিত করে আছে।
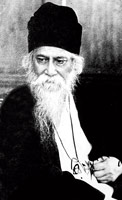 দু’টি ভাগ মিলে প্রবন্ধের সংখ্যা পঞ্চাশাধিক। ইংরেজি লেখাগুলিতে দেড়শো বছর ধরে রবীন্দ্রভাবনার নিরীক্ষা, মানবিতা ও নন্দনতত্ত্ব, বর্তমানের প্রেক্ষিতে কবির শিক্ষা ও দর্শনচিন্তা, তাঁর সমাজভাবনা, ঘর পার হওয়া কবি, তাঁর কৃষিভাবনা ও পল্লিসংগঠন, শিশুশিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ও রাদিচের পারস্পরিক অনুবাদে ‘জগৎ পারাবারের তীরে’, কবির গৃহস্থাপত্যবৈশিষ্ট্যে গড়া শান্তিনিকেতন, ফরাসি দেশে রবীন্দ্রনাথ ও গীতাঞ্জলি, অ্যালেক অ্যারনসন-বিতর্কিত তাঁর রচনা নিয়ে জার্মান গবেষকের সিদ্ধান্ত, চিত্রী রবীন্দ্রনাথ, ছোটগল্পে লিঙ্গ নির্ণয়ের মতো সাহসী ভাবন, বিজ্ঞানচিন্তা (কবির প্রথম গদ্যই তো বিজ্ঞান বিষয়ক), ড্যানিয়েল হ্যামিলটন সংযোগে, তাঁর ব্যক্তিস্পর্শী প্রেম (হেমন্তবালা চিঠি লেখেন রাত্রি দেড়টায়), রাজরোষক্লিষ্ট কবি পাসপোর্ট পেলেন না ১৯১৯-এর নাইট উপাধি ত্যাগের আগেও, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচিন্তা, গীতাঞ্জলি বনাম মানুষের ধর্ম, সব মিলিয়ে বিচিত্র ভাবনার একটা সিনথেসিস। দু’টি ভাগ মিলে প্রবন্ধের সংখ্যা পঞ্চাশাধিক। ইংরেজি লেখাগুলিতে দেড়শো বছর ধরে রবীন্দ্রভাবনার নিরীক্ষা, মানবিতা ও নন্দনতত্ত্ব, বর্তমানের প্রেক্ষিতে কবির শিক্ষা ও দর্শনচিন্তা, তাঁর সমাজভাবনা, ঘর পার হওয়া কবি, তাঁর কৃষিভাবনা ও পল্লিসংগঠন, শিশুশিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ও রাদিচের পারস্পরিক অনুবাদে ‘জগৎ পারাবারের তীরে’, কবির গৃহস্থাপত্যবৈশিষ্ট্যে গড়া শান্তিনিকেতন, ফরাসি দেশে রবীন্দ্রনাথ ও গীতাঞ্জলি, অ্যালেক অ্যারনসন-বিতর্কিত তাঁর রচনা নিয়ে জার্মান গবেষকের সিদ্ধান্ত, চিত্রী রবীন্দ্রনাথ, ছোটগল্পে লিঙ্গ নির্ণয়ের মতো সাহসী ভাবন, বিজ্ঞানচিন্তা (কবির প্রথম গদ্যই তো বিজ্ঞান বিষয়ক), ড্যানিয়েল হ্যামিলটন সংযোগে, তাঁর ব্যক্তিস্পর্শী প্রেম (হেমন্তবালা চিঠি লেখেন রাত্রি দেড়টায়), রাজরোষক্লিষ্ট কবি পাসপোর্ট পেলেন না ১৯১৯-এর নাইট উপাধি ত্যাগের আগেও, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচিন্তা, গীতাঞ্জলি বনাম মানুষের ধর্ম, সব মিলিয়ে বিচিত্র ভাবনার একটা সিনথেসিস।
স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে, এখানে রবীন্দ্রনাথ সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য নন, এখানে রবীন্দ্রনাথকে চেনা-জানার পালায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে, দুঃসাহসিক বিশ্লেষণ আছে। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে বুদ্ধদেব বসু একদা বিতর্ক করেছেন, কেতকী কুশারী ডাইসন-রা এবং এখন উইলিয়াম রাদিচে। ক্লিভল্যান্ড, হুইলার আর গ্রান্ডের গোপন চিঠিপত্রের নিরিখে রবীন্দ্রনাথকে দেখা— তাঁর ‘না-পসন্দ’ জীবনের আরও একটা বিদূষিত ইতিকথা। তথাকথিত সাহিত্য চর্চা নিয়ে তেমন লেখার সন্ধানীরা হতাশ হবেন। অজস্র এমনতর বইয়ের উপস্থিতির কথা ভেবেই হয়তো সম্পাদকেরা গ্রন্থভার আর বৃদ্ধি করতে চাননি। তবুও ‘গোরা’ আছে ‘ঘরে বাইরে’ আছে এবং আছে ছোটগল্পের আলোচনাও।
একতা-র সংযোজন একটা প্রাপ্তি বিশেষ। আদ্যঙ্গের সম্পাদনা-প্রকাশনার সঙ্গে একতা-র একটা পার্থক্য আছে। সূচনাপর্বের রচনাদির প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, একতা কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের পরিকল্পনা। ছাত্ররা এমনতর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এটা বর্তমান ছাত্রদের কাছে অনুসরণীয় উদাহরণ।
বইটির চিত্রসম্পদ, পাণ্ডুলিপিচিত্র সহ লোভনীয় এবং কিছুটা স্বতন্ত্র। বোঝাই যায়, সম্পাদকদ্বয় এ বিষয়ে স্বতন্ত্র রকমের চিন্তা করেছেন। নইলে একটি মূল বাংলা প্রবন্ধকে ইংরেজি অনুবাদে উপস্থাপিত করেছেন সম্ভবত এর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপ্ত প্রেক্ষিতের কথা ভেবে। একতা-য় ‘রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে (পৃ ১৮) একটি প্রমাদ: রামমোহনের মৃত্যুর বছরটি ‘১৮৮৩’ মুদ্রিত হয়েছে, সেটি হবে ১৮৩৩।
শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা ‘যুগান্তর’ উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে কাহিনি যে ভাবে গ্রাম থেকে শহর-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, তা লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— এর ফলে লেখক ‘পাঠকের রসভঙ্গ’ করেছেন এবং দুটি ‘পৃথক’ বইকে একত্রে বাঁধিয়ে দিয়ে ‘দপ্তরির অন্ন মারিয়াছেন’। বর্তমান বইটি রবীন্দ্রনাথের হাতে এলে তিনি এই মন্তব্য সম্ভবত কিছুটা সংশোধন করে বলতেন— এই মহান গ্রন্থে একতা-কে ঠাঁই দিয়ে সম্পাদকেরা পাঠকের ‘রসবর্ধন’ই করেছেন। এখনও এ দেশে সাহিত্যকর্মগুলি ‘লিটারেচার’-এর লোকেরাই সম্পাদনা করবেন— এমনতর ধারণা। সেই রীতি মেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি এবং বাংলা বিভাগের দুই ভাবুককে এর সম্পাদনাভার অর্পিত হয়েছে। সাহিত্য যে দর্শন এবং বিজ্ঞান— পৃথিবীর যাবতীয় ভাবনার বাহন— এটিই সম্পাদকদ্বয় নিঃশেষে প্রমাণ করেছেন। উপাচার্য, সহ-উপাচার্য এবং নিবন্ধকেরাও এতে শামিল হয়ে প্রথাগত শিক্ষাদান আর প্রশাসনের দুই মন্দিরাতে কালের সম্মিলন ঘটিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। |
|
|
 |
|
|