|
|
|
|
|
|
|
 |
পুস্তক পরিচয় ২... |
|
| মুক্তি হয়ত ঘটেছিল এই অভিঘাতেই |
| শিলাদিত্য সেন |
বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা/ ১৯২৩-৩৩/প্রথম খণ্ড, ঐ /১৯৩৪-৫৪/দ্বিতীয় খণ্ড।
সংকলন ও সম্পাদনা: দেবীপ্রসাদ ঘোষ। প্রতিভাস, ১৭৫.০০ ও ২২৫.০০ |
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন স্টুডিয়োতে গিয়ে শুটিং দেখছেন, ছবিটির পরিচালক ফ্রান্জ অস্টেন। মায়া, যে মেয়েটি নায়িকার ভূমিকায়, তাকে কাঁদতে হবে একটা দৃশ্যে। সে কান্নার ভঙ্গি করে বটে, কিন্তু তার চোখ দিয়ে জল বেরয় না। অস্টেন সাহেব তর্জন-গর্জন থেকে জার্মান ভাষায় গালমন্দ, সবই করলেন, এমনকী ‘মোটা একটা লাঠি এনে মাথার ওপর ঘোরাতে লাগলেন, কিন্তু মায়ার চোখ মরুভূমি।’ লিখেছেন শরদিন্দু। তখন অস্টেন সাহেব ‘কাঁদবে না! আচ্ছা মজা দেখাচ্ছি।’ এই হুংকার ছেড়ে তাকে ঠায় দাঁড় করিয়ে তার মুখের ওপর ক্যামেরা চালু করে দিলেন। ‘পাঁচ মিনিট পরে মায়ার চোখ দু’টি একটু ঝাপ্সা হয়ে গেল। তারপর দরদর ধারায় চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।’
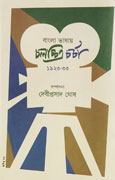 শরদিন্দুর এই লেখাটি বেরিয়েছিল ‘উল্টোরথ, ডিসেম্বর ১৯৫৪’-য়। বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা/ ১৯৩৪-৫৪-য় (দ্বিতীয় খণ্ড) রচনাটি গ্রন্থিত করেছেন সম্পাদক দেবীপ্রসাদ ঘোষ, গ্রহণের যুক্তি হিসেবে জানিয়েছেন: ‘তত্ত্বের চেয়ে বড়ো অভিজ্ঞতা যার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে নানান দিগ্দর্শন।’ এমন ‘দিগ্দর্শন’-এর নমুনা আরও আছে এ-খণ্ডে। পঁচাত্তর বছর আগের কোনও লেখা পড়ে তাই আজও অবাক হতে হয়, ‘চলচ্চিত্রের প্রচার কার্য’ নিয়ে সুধীরেন্দ্র সান্যালের রচনা, ‘চিত্রপঞ্জী’তে বেরিয়েছিল মাঘ ১৩৪২-এ। তাতে তিনি লিখছেন: “সর্বপ্রকার প্রচারকার্যের সর্বাপেক্ষা effective উপাদান হইতেছে ‘ছবি’। পিকটোরিয়াল পাবলিসিটি’র দ্বারা দর্শকচিত্তে সহজেই যে আকর্ষণ সৃষ্টি করা যায়, অপর কোনো উপায় তাহা সম্ভবপর নয়। কারণ, খুব ব্যস্তবাগিশ ব্যক্তিও কাগজে চোখ বুলাইয়া গেলে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় ছবির ওপর চোখের ইহা স্বাভাবিক ধর্ম।” এখনকার বিজ্ঞাপন-বিপণন জগতের সক্রিয় মানুষজনও ঠিক এ ভাবেই মাথা ঘামান সিনেমা নিয়ে, কী ভাবে সর্বসাধারণকে টেনে নিয়ে আসা যায় সিনেমা হলে। শরদিন্দুর এই লেখাটি বেরিয়েছিল ‘উল্টোরথ, ডিসেম্বর ১৯৫৪’-য়। বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা/ ১৯৩৪-৫৪-য় (দ্বিতীয় খণ্ড) রচনাটি গ্রন্থিত করেছেন সম্পাদক দেবীপ্রসাদ ঘোষ, গ্রহণের যুক্তি হিসেবে জানিয়েছেন: ‘তত্ত্বের চেয়ে বড়ো অভিজ্ঞতা যার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে নানান দিগ্দর্শন।’ এমন ‘দিগ্দর্শন’-এর নমুনা আরও আছে এ-খণ্ডে। পঁচাত্তর বছর আগের কোনও লেখা পড়ে তাই আজও অবাক হতে হয়, ‘চলচ্চিত্রের প্রচার কার্য’ নিয়ে সুধীরেন্দ্র সান্যালের রচনা, ‘চিত্রপঞ্জী’তে বেরিয়েছিল মাঘ ১৩৪২-এ। তাতে তিনি লিখছেন: “সর্বপ্রকার প্রচারকার্যের সর্বাপেক্ষা effective উপাদান হইতেছে ‘ছবি’। পিকটোরিয়াল পাবলিসিটি’র দ্বারা দর্শকচিত্তে সহজেই যে আকর্ষণ সৃষ্টি করা যায়, অপর কোনো উপায় তাহা সম্ভবপর নয়। কারণ, খুব ব্যস্তবাগিশ ব্যক্তিও কাগজে চোখ বুলাইয়া গেলে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় ছবির ওপর চোখের ইহা স্বাভাবিক ধর্ম।” এখনকার বিজ্ঞাপন-বিপণন জগতের সক্রিয় মানুষজনও ঠিক এ ভাবেই মাথা ঘামান সিনেমা নিয়ে, কী ভাবে সর্বসাধারণকে টেনে নিয়ে আসা যায় সিনেমা হলে।
প্রথম খণ্ডটিতেও (১৯২৩-৩৩) সম্পাদক এই ‘নানান দিগ্দর্শন’-কেই অবলম্বন করেছেন। প্রথম খণ্ডের রচনাগুলি আবার নির্বাক ও সবাক এই দুই যুগে বিন্যস্ত। সব মিলিয়ে সময়সীমা ১৯২৩-৫৪, স্বাধীনতা-পূর্ব আর উত্তর দু’টি পর্বই ছুঁয়েছে লেখাগুলি।
আসলে স্বাধীনতা পাওয়ার কিছু বছর আগে মাত্র সিনেমার সঙ্গে আমাদের পরিচয়। অথচ কবিতা-নাটক-গল্প-উপন্যাস-চিত্রকলা-ভাস্কর্য-সংগীত-নৃত্য-অভিনয় এ-সমস্ত শিল্পরূপের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, সেখানে সিনেমা শুধু নতুনই নয়, পশ্চিমি অভিঘাতে পাওয়া। তার ওপর আবার সিনেমা আপাদমস্তক যন্ত্রনির্ভর। যন্ত্রের সঙ্গে আত্মীয়তা তৈরি করা, আর একই সঙ্গে ফিল্ম-এর শিল্পরূপ নির্ণয় করা কঠিন ছিল বড়। হাতে-কলমে ছবি তৈরির পাশাপাশি তখন জরুরি হয়ে উঠেছিল কাগজে-কলমেও ফিল্ম নিয়ে নিরন্তর চর্চা, যেখানে সিনেমায় আধুনিকতার বোধ বা তাতে দেশকাল-জনিত চিন্তাভাবনার খোঁজ অচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে বাঁধা পড়তে পারে। দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতে ‘প্রসঙ্গ কথা’য় সম্পাদক স্বীকারও করেছেন : ‘নিবন্ধগুলির মধ্যে বরাবর একটি সরলরেখা ছুঁয়ে গেছে। সেটি জাতীয়তা বোধ।’
যেমন ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২-এর ‘নাচঘর’ পত্রিকায় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ‘দেশি ছবির দর্শক’ সম্পর্কে লিখছেন: ‘গ্যালারির মুখ চাহিয়া ছবি তুলিতে ফিল্ম কোম্পানিকে যতই আমরা নিষেধ করি না কেন, তাঁদের সে-কথায় কর্ণপাত করিবার আশা আমরা ততদিন কিছুতেই করিতে পারি না যতদিন না বাঙালি দর্শক উঁচুদরের নিঁখুত ছবির কদর না করেন।’ বোঝাই যাচ্ছে ভাল ছবি দেখার জন্যে দর্শককে দীক্ষিত হতে পরামর্শ দিচ্ছেন সৌরীন্দ্রমোহন। উল্টোদিকে আবার বুদ্ধদেব বসুর অভিযোগটা ছবি-করিয়েদের প্রতি। শ্রাবণ ১৩৪০-এর ‘চিত্রপঞ্জী’তে তাঁর লেখা ‘সিনেমা কেন দেখি না’-তে তিনি স্পষ্টই জানাচ্ছেন, দেবকীকুমার বসু পরিচালিত নিউ থিয়েটার্স-এর ‘চণ্ডীদাস’ তিনি দেখেননি, কারণ তাঁর ‘দেখার ইচ্ছেও কখনও হয়নি।’ লিখেছেন ‘জাগ্রত বুদ্ধি লোকের জন্য ফিল্ম যে তৈরি হতে না পারে তা নয় হয়েও থাকে। কিন্তু তার সংখ্যা এত ওঃ, এত কম!’
দু’টি খণ্ড জুড়ে নিবন্ধাদিতে এই যে আপাত বিপরীতের টান, তাকে ধারণ করে থাকে এক সমগ্রতার আভাস, সমগ্রতার সেই আধার ব্যতীত সিনেমার শিল্পরূপের আধুনিকতা কিংবা তার স্বদেশজিজ্ঞাসা আয়তন পায় না।
চলচ্চিত্রকার দেবকীকুমার বসু তাঁর রচনা ‘ছবি সম্পর্কে সতর্ক হোন’-এ (চিত্রবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮) লিখছেন “দাবি করুন ‘পাবলিক সেন্সর সার্টিফিকেট’ ব্যবস্থার, যাতে সুস্পষ্ট চিহ্নিত থাকে ‘ছবি সম্পর্কে সতর্ক হোন’ সেইসব ছবির ওপর যেগুলির উদ্দেশ্য এই সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন থেকে আমাদের ছিনিয়ে নেওয়া।’’ আর ‘নবশক্তি’তে ৩০ নভেম্বর ১৯৩৪-এ ‘চিত্রশাসক সমিতি’ সম্পর্কে নরেন্দ্র দেব লিখছেন “চলচ্চিত্র শিল্পের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হয়ে উঠছেন চিত্রশাসক সমিতি বা সেন্সার কর্তৃপক্ষ।... আমাদের দেশেও এই ‘সেন্সারে’র উৎপাত সুরু হয়েছে।’’
পরাধীন অবস্থা থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর অবধি বিদ্বজ্জনেদের ভিতর এই যে বিতর্ক, এ আসলে বহুস্বরেরই লক্ষণ। না মেনে উপায় নেই যে অত্যন্ত সুলক্ষণ। হয়তো এই অভিঘাতেই বাংলা তথা ভারতীয় ছবির মুক্তি ঘটেছিল সত্যজিতের হাতে। খেয়াল করুন, বইটির সময়সীমা শেষ হচ্ছে ১৯৫৪-য়, আর ১৯৫৫-য় মুক্তি পেল ‘পথের পাঁচালী’। |
|
|
 |
|
|