|
|
|
|
|
|
|
 |
পুস্তক পরিচয় ১... |
|
| দেশভাগের না-বোঝা ছবির খোঁজে |
| সেমন্তী ঘোষ |
পার্টিশন্ড লাইভস/ মাইগ্রান্টস, রিফিউজিস, সিটিজেন্স ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান, ১৯৪৭-১৯৬৫,
হৈমন্তী রায়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ৬৯৫.০০
রিকনস্ট্রাক্টিং দ্য বেঙ্গল পার্টিশন/ দ্য সাইকি আন্ডার আ ডিফারেন্ট ভায়োলেন্স, জয়ন্তী বসু। সাম্য, ৬৫০.০০ |
দেশভাগ শব্দটা বহু-ব্যবহারজীর্ণ, তবুও বড় জটিল। আমাদের মনে দেশভাগ বলতেই কিছু ছবি ভেসে ওঠে। অথচ দেশভাগের অভিজ্ঞতায় যাঁরা সরাসরি যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মনের মধ্যে সম্ভবত ওই সুনিটোল ছবিগুলি নেই! তাঁদের আছে অন্য অসংখ্য ছবি, ধূসর, এলোমেলো, কোনওটা অস্পষ্ট, কোনওটা অতি স্পষ্ট। যা-ই হোক না কেন, সেগুলো এই পরপ্রজন্মের ছবির থেকে অনেক আলাদা। খুব বড় ধ্বংসকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যাঁরা নিজেরা হেঁটে আসেন, আর পরে যাঁরা সেই ধ্বংসের ইতিহাস শোনেন জানেন লেখেন বলেন, তাঁদের মধ্যে এইখানে একটা বিরাট ব্যবধান থেকে যায়। ব্যবধানটা দূর করা না গেলেও কমানো যায় নিশ্চয়ই। সেই কমাতে পারার মধ্যেই থাকে ইতিহাসের সন্ধান এবং ইতিহাসের শিক্ষা।
হৈমন্তী রায় এবং জয়ন্তী বসু, এক জন ইতিহাসবিদ, অন্য জন মনস্তত্ত্ববিদ। দু’জনেই ঠিক এখান থেকে খুঁজে পেয়েছেন দেশভাগ নিয়ে চর্চার যুক্তি। তাঁদের প্রশিক্ষণ আলাদা, পদ্ধতি আলাদা, প্রশ্নগুলোও আলাদা, কিন্তু অনুপ্রেরণাটা এক। দুটি গবেষণাই পুনর্নির্মাণ করতে চায় দেশভাগের অভিজ্ঞতা: জয়ন্তীর ভাষায়, “.. reconstruct from their reconstructions the very special period in history...”। এইটুকু সাদৃশ্যের পরই কিন্তু সম্পূর্ণ দুই বি-সদৃশ, এমনকী বিপরীত পথে হাঁটে তাঁদের অনুসন্ধান। এক জন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তৈরির চেষ্টা করেন একটা বড় সামাজিক-রাজনৈতিক ছবি। অন্য জন, মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির জট ছাড়িয়ে দেশভাগের ফলে তৈরি মানস-জাগতিক ওলটপালটের হদিশ পেতে চান।
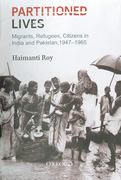 ১৯৫২ সালে মালদহ ও রাজশাহির সীমান্তে কিছু মানুষ ধান বুনছেন, এমন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের দিক থেকে কিছু সীমান্তরক্ষী ঢুকে পড়লেন, সঙ্গে মৌলবি করিম শাহ নামে রাজশাহির এক ‘পাকিস্তানি নাগরিক’। দাবি: ওই জমি মালদহের লোকেরা চাষ করতে পারে না, জমিটা মৌলবির। ব্যাপারটা কেবল স্বল্পশিক্ষিত স্বল্প-অবহিত গ্রামীণ মানুষের সীমান্ত-বিভ্রান্তি হয়ে রইল না, আরও বড় আকার নিল, শুরু হল সরকারি চাপান-উতোর। হল বটে, কিন্তু সেই সরকারি তর্কাতর্কি কোনও আন্তর্জাতিক সংকটও তৈরি করল না। আরও অসংখ্য সীমান্ত-বিতর্কের সঙ্গে স্থানীয় অফিসারদের অমীমাংসিত সংঘর্ষের তালিকাতেই চিরকালীন স্থান করে নিল বিষয়টি। হৈমন্তীর উদ্ধৃত বহু ঘটনার মধ্যে এটিও একটি। ১৯৫২ সালে মালদহ ও রাজশাহির সীমান্তে কিছু মানুষ ধান বুনছেন, এমন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের দিক থেকে কিছু সীমান্তরক্ষী ঢুকে পড়লেন, সঙ্গে মৌলবি করিম শাহ নামে রাজশাহির এক ‘পাকিস্তানি নাগরিক’। দাবি: ওই জমি মালদহের লোকেরা চাষ করতে পারে না, জমিটা মৌলবির। ব্যাপারটা কেবল স্বল্পশিক্ষিত স্বল্প-অবহিত গ্রামীণ মানুষের সীমান্ত-বিভ্রান্তি হয়ে রইল না, আরও বড় আকার নিল, শুরু হল সরকারি চাপান-উতোর। হল বটে, কিন্তু সেই সরকারি তর্কাতর্কি কোনও আন্তর্জাতিক সংকটও তৈরি করল না। আরও অসংখ্য সীমান্ত-বিতর্কের সঙ্গে স্থানীয় অফিসারদের অমীমাংসিত সংঘর্ষের তালিকাতেই চিরকালীন স্থান করে নিল বিষয়টি। হৈমন্তীর উদ্ধৃত বহু ঘটনার মধ্যে এটিও একটি।
আপাত ভাবে সাধারণ হলেও এমন ঘটনার মধ্য দিয়ে হৈমন্তী দুটো কথা বুঝিয়ে দেন: এক, দেশভাগ বলতে যে ছবিই আমাদের মনে আঁকা থাকুক না কেন, সেই ছবির নিটোলতা কেবল সে দিন নয়, আজও পায়নি এই ত্রি-বিভক্ত উপমহাদেশ। আর পায়নি বলেই সীমান্তের সব দিকেই জীবন সমানে নতুন সংকটের মুখোমুখি হয়ে চলেছে, যার খবর অনেক সময় রাষ্ট্রের উচ্চতম স্তর অবধি পৌঁছয় না, সমাজেই বিধৃত থেকে যায়, কিন্তু সমাজও শেষ পর্যন্ত যার মীমাংসা করতে পারে না। আর তাই হৈমন্তী বলেন, প্রথম থেকেই দেশভাগ-পরবর্তী রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ‘সীমান্ত’-র থেকে অনেক অর্থপূর্ণ হল ‘সীমাঞ্চল’। জাতীয় স্তরে প্রথম থেকে নানা নীতি-নির্ধারণ সত্ত্বেও সীমারেখার দুই দিকেই সরকারি নীতিতে এই সীমাঞ্চলের সমস্যা একটা স্থায়ী ক্ষত হয়ে থেকে যায়।
দুই, বিভক্ত রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের মধ্যে এই যে রোজকার অনিশ্চিতি, তার ছবিটি স্পষ্ট হয় সরকারি উঁচুমহলের নথিপত্রের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নীচের নানা স্তরের তথ্য-বর্ণনা-বিবরণের মধ্যে, সংখ্যালঘু সমাজ কিংবা উদ্বাস্তু শিবিরের গল্পকাহিনি বা স্মৃতিরোমন্থনের মধ্যে বেরিয়ে এলে। হৈমন্তীর বই-এর বিরাট গুণ, এই ভাবে সরকারি-অসরকারি উঁচু-নিচু ব্যক্তি-গোষ্ঠী সামাজিক-রাষ্ট্রিক নানা তথ্যের অর্থময় সমাহার ঘটানো। এইখানেই তিনি নিজেকে আলাদা করে নেন সমসাময়িক আর এক খ্যাতিমান ইতিহাসবিদের থেকে। জয়া চ্যাটার্জির স্পয়েলস অব পার্টিশন ১৯৪৭-পরবর্তী বাংলার যে ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল, তার ভরটা কিন্তু ছিল কেবলই উচ্চ সরকারি রাজনীতির উপর। অবশ্য এও ঠিক, হৈমন্তী এক একটি অধ্যায়ে এক এক ধরনের উপাদানের উপর জোর দেন। ব্যক্তিগত উপাদানের ব্যবহার ‘উদ্বাস্তু’ অধ্যায়ে যতখানি, ‘নাগরিক’ অধ্যায়ে তার চেয়ে অনেকটাই কম। তবে এমন পদ্ধতিগত সমস্যা তো ইতিহাস-রচয়িতার আবশ্যিক সঙ্গী।
হৈমন্তীর গবেষণায় আরও একটা বড় পার্থক্য রয়েছে জয়া চ্যাটার্জির বই থেকে। দেশভাগের দায়িত্ব তিনি কংগ্রেসি (হিন্দু) নেতৃত্বের দিকে ঠেলে দেননি, দেশভাগের ফলাফল বিচারের সময়ও তিনি জয়া চ্যাটার্জির মতো কংগ্রেস নেতাদের পারস্পরিক হিসেবনিকেশ এবং হতাশা-প্রতিযোগিতার চক্রে আবদ্ধ থাকেননি। তাঁর গবেষণার ফোকাস সম্পূর্ণ ভিন্ন: সীমান্ত, উদ্বাস্তু ও সংখ্যালঘু সমস্যা এবং ‘আইডেন্টিটি’ রাজনীতির বিকাশ। তবে এই সূত্রে অন্য একটা গুরুতর প্রশ্ন উঠে আসে। ভূমিকায় তিনি দাবি করেছেন, ১৯৪৭-কে নিশ্চিত ‘ব্রেক’ বা সূচনাবিন্দু হিসেবে না দেখে আগের আর পরের ইতিহাসের মধ্যে একটা বহমানতা তৈরি করা জরুরি। আবার পরে তিনি নিজেই পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে ‘১৯৪৭’-এর গুরুত্ব হ্রাস করে দেখানোর প্রবণতার বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেছেন, সেখানে বাংলাদেশি মুসলমান সত্তার ‘ইতিহাস’ এক আশ্চর্য নিপুণতায় ’৪৭-পূর্ব যুগ থেকেই ‘নির্মাণ’ করা শুরু হল! তাঁর আপত্তির কারণটা বোঝা গেল না, কারণ সত্যিই তো বাঙালি মুসলমান সত্তা ’৪৭-পরবর্তী ঘটনা নয়, অনেক পুরনো তার উৎস! হৈমন্তীর বিক্ষিপ্ত মন্তব্যে সেই উৎসের কোনও সন্ধান নেই।
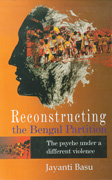 সীমাঞ্চলের সংকটের মতোই দেশভাগের মনোজাগতিক ক্ষতও আজও প্রত্যহের বাস্তব। পঞ্জাবের তুলনায় বাংলায় দেশভাগের অভিজ্ঞতায় হিংসার তীব্রতা কম: অনেক শোনা কথা। কিন্তু হিংসার তীব্রতা কম হলেই হিংসার জন্য মানসিক ক্ষতির পরিমাণ কম হয় না। বরং, অনেক ক্ষেত্রেই অনতিতীব্র হিংস্র পরিস্থিতির দীর্ঘকালীন ক্ষয় গভীরতর হয়। বাঙালির ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে, বলেন জয়ন্তী বসু। এই অনুচ্চ হিংসার দীর্ঘ ইতিহাসকে তিনি নাম দেন ‘soft violence’। এই আলাদা গোত্রের হিংসার সামাজিক প্রভাবও আলাদা, সেখানে প্রকাশ্য ক্ষতের থেকে প্রচ্ছন্ন ক্ষতি বেশি হয়। সীমাঞ্চলের সংকটের মতোই দেশভাগের মনোজাগতিক ক্ষতও আজও প্রত্যহের বাস্তব। পঞ্জাবের তুলনায় বাংলায় দেশভাগের অভিজ্ঞতায় হিংসার তীব্রতা কম: অনেক শোনা কথা। কিন্তু হিংসার তীব্রতা কম হলেই হিংসার জন্য মানসিক ক্ষতির পরিমাণ কম হয় না। বরং, অনেক ক্ষেত্রেই অনতিতীব্র হিংস্র পরিস্থিতির দীর্ঘকালীন ক্ষয় গভীরতর হয়। বাঙালির ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে, বলেন জয়ন্তী বসু। এই অনুচ্চ হিংসার দীর্ঘ ইতিহাসকে তিনি নাম দেন ‘soft violence’। এই আলাদা গোত্রের হিংসার সামাজিক প্রভাবও আলাদা, সেখানে প্রকাশ্য ক্ষতের থেকে প্রচ্ছন্ন ক্ষতি বেশি হয়।
প্রকাশ্য ক্ষতির বিচার সংখ্যায় হয়, প্রচ্ছন্ন ক্ষতির ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। প্রচ্ছন্ন ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানগুলিকে ঠিক ভাবে বুঝতে পারাই কঠিন কাজ। কতটা কঠিন, একটি বাক্যের অসামান্য ব্যঞ্জনায় বুঝিয়ে দেন জয়ন্তী। তাঁর বাবা থেকে শুরু করে কত জনের মুখে দেশভাগের কথা শুনতে বসে তিনি আক্ষেপ শুনেছেন, ‘কিসুই বোঝস নাই’। সেই প্রজন্মের পুরনোকে হারানো ও নতুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যন্ত্রণা, আমাদের না-বোঝা যন্ত্রণা, যে ভাবে মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে চেয়েছেন জয়ন্তী, দেশভাগের গবেষণায় তা সত্যিই অ-ভূতপূর্ব ।
মনোবিশ্লেষণের শিক্ষক জয়ন্তী প্রথমেই সতর্ক করে দেন, হয়তো আমরা কেবল বুঝতে পারি দেশভাগের স্মৃতিটাকেই দেশভাগকে নয়: “Partition means what Partition is in one’s mind’s mirror”। ঘটনা আর ঘটনার স্মৃতির মধ্যে এই প্রতিসরণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন তিনি: কী ভাবে ব্যক্তির নিজস্বতা স্মৃতির মধ্যে স্পষ্ট ছাপ ফেলে যায়, কী ভাবে ‘self’ বা ‘আত্ম’-র নির্মাণ একদম ভিন্ন পথ ধরে ‘ট্রমা’-দীর্ণ মানুষের ক্ষেত্রে, কী ভাবে তাঁদের সত্তা অনেক ক্ষেত্রে ‘নিজের’টুকুর বদলে হঠাৎই যূথস্মৃতি হয়ে দাঁড়ায়, কী ভাবে এঁদের চেতনায় নিহিত ‘আতঙ্ক’ তৈরি করে তোলে নিরাপত্তার নিত্য ব্যবহারিক অভাববোধ। এমনকী সাক্ষাৎকারের সময় কী ভাবে মিশে যায় সাক্ষাৎকারীর নিজের subjectivity বা নিজস্বতা, এবং একটি মিশ্র বয়ান তৈরি হয়ে ওঠে শেষে। আশিস নন্দীর অনুসরণে মানবমনের যে আলো-আঁধারির আলোচনায় তিনি আমাদের টেনে নিয়ে যান, তা একটি গবেষণা-পদ্ধতি হিসেবে একেবারে নতুন আলাদা গোত্র: দেশভাগ সেখানে নেহাতই গৌণ উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। তবে প্রশ্ন ওঠে: যে কোনও বয়ানেই যদি এতগুলি প্রতিসরণের স্তর থাকে, তা হলে কোনও বিশ্লেষণই কি চূড়ান্ত হওয়া সম্ভব? বস্তুত, জয়ন্তীর মনোবিশ্লেষণে এতগুলি শর্ত ও এতগুলি ভাবনা থেকে যায় যে মাঝেমধ্যে পথ হারিয়ে ফেলা ছাড়া গতি নেই। গভীরতর স্তরে টেনে নিয়ে যান বলে গভীর সংশয়ও তৈরি হতে থাকে। এই যে ব্যক্তিসাপেক্ষ গবেষণা-পদ্ধতি, ইতিহাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঠিক কী রকম? ‘দেশভাগের বাস্তবতা’র সঙ্গে ‘দেশভাগের স্মৃতি’র তা হলে কি আদৌ কোনও যোগ আছে? না কি ‘দেশভাগের স্মৃতি’ই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক?
প্রশ্ন থাকল। কিন্তু সঙ্গে একটা বিরাট আশ্বাসও থাকল। দেশভাগের সামাজিক ও মানসিক ওলটপালটের যে ছবিগুলির সঙ্গে আমরা আজও তত পরিচিত নই, সেগুলির নতুন রকম অনুসন্ধান হয়ে চলেছে। হৈমন্তী ও জয়ন্তী, দু’জনেই সেই আশ্বাস। |
|
|
 |
|
|