|
|
|
|
|
|
|
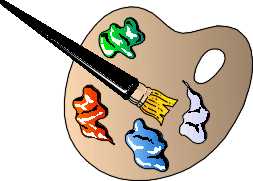 |
চিত্রকলা ও ভাস্কর্য ১... |
|
| পরিস্ফুট হয়েছে শিল্পীর নিজস্ব যন্ত্রণা ও দায়বোধ |
| আকার প্রকারে অনুষ্ঠিত হল গোপাল ঘোষের একক প্রদর্শনী। লিখছেন মৃণাল ঘোষ |
কয়েক মাস আগে গোপাল ঘোষের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে তাঁর ছবির একটি বড় মাপের প্রদর্শনী হয়েছিল দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারিতে। প্রদর্শনীটি পরিকল্পনা বা কিউরেট করেছিলেন বিশ্বভারতী কলাভবনের শিল্প-ইতিহাসের অধ্যাপক ড. সঞ্জয়কুমার মল্লিক। এই উদ্যোগে অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে কলকাতার আকার প্রকার গ্যালারিরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁদেরই প্রয়াসে এই গ্যালারিতে সম্প্রতি দেখানো হল এই প্রদর্শনীর একটি বড় অংশ। প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি সমৃদ্ধ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গোপাল ঘোষের শিল্পীব্যক্তিত্বের উন্মোচনে এবং তথ্য পঞ্জীকরণের দিক থেকে গ্রন্থটি খুবই সহায়ক। ১৯৩০-এর দশক থেকে ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ভাগ করে প্রদর্শনীতে এবং স্মারকগ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর ছবি। তাঁর বিবর্তন বুঝতে সেটা খুবই সহায়ক।
গোপাল ঘোষকে বলা যেতে পারে ১৯৪০-এর দশকে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত শিল্পী। ১৯৪৩ সালে, মন্বন্তরের বছর, কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ‘ক্যালকাটা গ্রুপ’। এই গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৪৮ পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন এই দলের সঙ্গে। এই দলের প্রত্যেক শিল্পীর প্রকাশভঙ্গি আলাদা হলেও একটি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে ঐক্য ছিল। স্বাভাবিকতাবাদী চিত্রধারা ও নব্য ভারতীয় ধারার অতীতচারিতাকে অতিক্রম করে তাঁরা সমাজবাস্তবতাভিত্তিক আধুনিকতাবাদী আঙ্গিক গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্য আধুনিকতা, দূর প্রাচ্যের উত্তরাধিকার এবং ভারতীয় লৌকিক থেকে রসদ সংগ্রহ করে, তাকে সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে নিজস্ব রূপকল্প উদ্ভাবন করেছেন তাঁরা। |
 |
| শিল্পী: গোপাল ঘোষ |
নিসর্গচিত্রেই এই শিল্পী নিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর সমগ্র মনন। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, রবীন্দ্রনাথ, বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্করে আমাদের নিসর্গরচনার যে ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ সেখানে একটি নতুন পরিসর তৈরি করেছেন আলোচ্য শিল্পী। উপরোক্ত কোনও শিল্পীর কাজের সঙ্গেই তাঁর কোনও মিল নেই। চিত্রকলায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা জয়পুরে শৈলেন্দ্রনাথ দে ও মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর অধীনে। তা সত্ত্বেও নব্য-ভারতীয় ধারার প্রভাবকে তিনি খুব সফল ভাবে পরিহার করতে পেরেছেন। পাশ্চাত্যের প্রতিচ্ছায়াবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ এবং চিন-জাপানের নিসর্গরচনার প্রজ্ঞা হয়ে উঠেছে তাঁর নিসর্গের প্রধান এক প্রস্থানবিন্দু। দৃশ্যের প্রত্যক্ষ বর্ণনাকে পরিহার করে তিনি এর নিহিত সংবিৎকে ধরতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর ছবি হয়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব চেতনার নিসর্গ।
এই প্রদর্শনী আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, নিসর্গেই সীমাবদ্ধ ছিল না তাঁর প্রকাশ। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের বাস্তবতার অন্যতম রূপকার ছিলেন তিনিও। জীবনের এই অন্ধকার দিক তাঁকে ভাবিয়েছে। নিসর্গের মধ্যেও এই ছায়াচ্ছন্নতার প্রকাশ এসেছে অনেক সময়। নিসর্গের পাশাপাশি তিনি সারা জীবনই এঁকে গেছেন মানুষের মুখ ও অবয়ব, পাখি ও বিভিন্ন স্থিরবস্তু চিত্র। তাঁর সব সময়ই প্রবণতা ছিল রূপের সংক্ষিপ্তকরণের দিকে। ইংরেজিতে যাকে ‘মিনিমাল’ বলা যেতে পারে।
যে ছবিটি দেখছি আমরা এই লেখার সঙ্গে সেটি ১৯৪৬-এ আঁকা একটি জলরঙের রচনা। তখনকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি আলেখ্য। পথের উপর একটি গাড়িতে আগুন জ্বলছে। দূরে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছে। দৃশ্যের অনুপুঙ্খ বর্ণনা নেই। আভাসটুকু আছে মাত্র। তাতেই বাস্তবতার ভয়াবহতা পরিস্ফুট হয়েছে। অভিব্যক্ত হয়েছে শিল্পীর নিজস্ব যন্ত্রণা ও দায়বোধও। মন্বন্তরের ছবিও তিনি অনেক এঁকেছেন।
তাঁর ১৯৩০-এর দশকের অনেক ছবিতে নব্য ভারতীয় ধারার কিছু প্রভাব দেখা যায়। চৈনিক তুলিচালনার রীতিও অনুশীলন করেছেন। ১৯৩৭-এ তিনি সাইকেলে ভারত ভ্রমণ করেন। দেশকে জানার এই ছিল এক অভিনব উদ্যোগ। এই প্রকল্পে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি লিখে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। চল্লিশের দশকের বাস্তবতা তাঁকে স্বতন্ত্র জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নিসর্গে আসছিল সুন্দরের এক উদ্দীপিত রূপ। পঞ্চাশের দশকে কোথাও কোথাও নিসর্গ ও জীবনকে মেলাচ্ছেন। ১৯৫৫-র একটি জলরঙের ছবিতে দেখি, ফসলের ক্ষেতে কর্মমগ্ন দুই গ্রামীণ মানবীকে। জীবন নিসর্গকে নতুন মাত্রায় ব্যঞ্জিত করছে। এই ব্যঞ্জনাই প্রসারিত হয়েছে ষাট ও সত্তরের দশক জুড়ে। ১৯৭১-এর একটি ছবিতে দেখি তমসামগ্ন পরিমণ্ডলে ফুটে আছে কিছু লাল ফুল। অন্ধকারের ভিতর থেকে এই আলোর জীবনেই তিনি জীবনকে নন্দিত করেছেন। |
|
|
 |
|
|