|
|
|
|
|
|
|
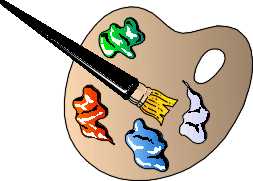 |
চিত্রকলা ও ভাস্কর্য ১... |
|
| নানা দিগন্তে বিস্তৃত আধুনিকতার চেতনা |
| সম্প্রতি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে অনুষ্ঠিত হল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি নিয়ে প্রদর্শনী। লিখছেন মৃণাল ঘোষ। |
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬৭-১৯৩৮) ছবি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মনোজ্ঞ প্রদর্শনী হল সম্প্রতি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। প্রদর্শিত এই ১০৮টি ছবি রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংগ্রহের অন্তর্গত। ১৯১১ থেকে ১৯২৫-৩০-এর মধ্যে এগুলি আঁকা হয়েছিল। ফলে শিল্পীর বিবর্তনের একটা রূপরেখা উঠে আসে এই প্রদর্শনী থেকে। ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করে ছবিগুলি সাজানো হয়েছে।
পর্যায়গুলি হল-
১. গোড়ার দিকের স্কেচ বা রেখাচিত্র,
২. ‘জীবনস্মৃতি’ পর্যায়ের জাপানি প্রকরণের ছবি,
৩. চৈতন্য চরিত্রমালা,
৪. মহাভারতের দৃশ্য, হিমালয়ের নিসর্গ ও রাত্রির আবহভিত্তিক ছবি,
৫. কার্টুন বা ক্যারিকেচার পর্যায়ের রচনা,
৬. কিউবিজমের অনুষঙ্গের রূপারোপ।
এই পর্যায়গুলো দেখলে বোঝা যায়, গগনেন্দ্রনাথ নানা আঙ্গিকে, নানা বিষয়ে, নানা ভাবনা ও উত্তরাধিকার আত্মস্থ করে কাজ করেছেন। এই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁর আধুনিকতার চেতনা নানা দিগন্তে বিস্তৃত হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, তাঁর সমাজচেতনা, শিল্পকলার আবিশ্ব উৎস সম্পর্কে সচেতনতা ও আত্মস্থ করার প্রয়াস তাঁর ছবিতে অন্য এক বোধ উৎসারিত করেছিল, যা তাঁর সমসাময়িক অন্য কোনও শিল্পীর মধ্যে ছিল না।
এই প্রদর্শনীর স্মারকপত্রে বলা হয়েছে গগনেন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতের একজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী। যিনি ভারতীয় শিল্পে আধুনিকতা এনেছিলেন। (‘হু হ্যাজ ব্রট মডার্নিটি টু ইন্ডিয়ান আর্ট’)। এ উক্তির মধ্যে অর্ধসত্য আছে। কেননা আধুনিকতার প্রথম উন্মোচন তো ঘটেছিল আরও আগে, স্বাভাবিকতাবাদী শিল্পীদের কাজে এবং তার পর পরিপূর্ণ মাত্রায় অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে। সেই ধারাবাহিকতায় গগনেন্দ্রনাথের অবস্থান যে স্বতন্ত্র, এটা অনুধাবনের প্রয়োজন আছে।
গগনেন্দ্রনাথ নব্য-ভারতীয় ঘরানার সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট’-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। কিন্তু নিজের ছবিতে তথাকথিত পুনরুজ্জীবনবাদী ভারতীয়তাকে প্রশ্রয় দেননি। নানা ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করে পরিব্যাপ্ত করেছেন আধুনিকতার চেতনা।
|
 |
| শিল্পী: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর |
পরিপূর্ণ ভাবে তিনি ছবি আঁকা শুরু করেছেন অনেক দেরিতে। মোটামুটি ভাবে ১৯০৫ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর সৃজনময় জীবন। ১৯৩০-এ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে আর কাজ করতে পারেননি। এই ২৫ বছরে তিনি অবশ্য অনেক ছবি এঁকেছিলেন। তার সামান্য অংশই এখন অবশিষ্ট আছে। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার আগুনে তাঁর মেয়ের বাড়িতে নষ্ট হয়েছে অজস্র ছবি। জাহাজডুবিতেও হারিয়ে গেছে অনেক। জানিয়েছেন চণ্ডী লাহিড়ি গগনেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত তাঁর বইতে। এখন যা অবশিষ্ট আছে, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তাও খুব ভাল অবস্থায় নেই।
১৯০৫ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে চাইনিজ ইঙ্কে তিনি কিছু কাকের ছবি আঁকেন। জাপানি কালি-তুলির ছাপ ছিল এতে। ১৯০২ সালে জাপানি মনীষী ওকাকুরা এসেছিলেন কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন তিন জন শিল্পী তাইকান, কাৎসুতা ও হিশিদা শুনসো। তাঁদের সংস্পর্শে এসে গগনেন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হন জাপানি আঙ্গিকের প্রতি। এই পর্যায়ের ছবি মাত্র একটি এই প্রদর্শনীতে ছিল। এখানে শুরু হয়েছে ১৯০৯-এর কিছু মুখাবয়ব রচনা দিয়ে। কুমারস্বামী ও হুক্কায় ধূমপানরত অবনীন্দ্রনাথের মুখাবয়ব দুটি উল্লেখযোগ্য। জাপানি আঙ্গিকের অনবদ্য প্রকাশ দেখা যায় ১৯১১-র বাঁশপাতার ছবিতে।
১৯১১-১২-তে আঁকা ‘জীবনস্মৃতি’-র সচিত্রকরণের ছবি গগনেন্দ্রনাথের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। গ্রন্থচিত্রণের একটি আদর্শ যেমন তৈরি হয়েছে এই ছবিতে তেমন বর্ণের বিরলতায় অন্তর্দীপ্ত গভীর অনুভবের উৎসারণও ঘটেছে এর মধ্যে। পুরাণকল্পকে গগনেন্দ্রনাথ কেমন করে ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ করেছেন, তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন ১৯১২-১৩-র ‘চৈতন্য-র স্বর্গীয় প্রেমের প্রথম অভিজ্ঞতা’ শীর্ষক ছবিটি। পাশ্চাত্য প্রতিচ্ছায়াবাদী রীতি, জাপানি কালি-তুলির পদ্ধতি ও দেশীয় প্রথাগত চিত্ররীতির অসামান্য সংশ্লেষ ঘটেছে এই ছবিতে। এই সংশ্লেষ পদ্ধতির ভিতর দিয়েই গগনেন্দ্রনাথ আমাদের আধুনিকতায় নতুন উত্তরণ এনেছেন, যার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমরা দেখি তাঁর তথাকথিত ঘনকবাদী ছবিতে।
এখানে কিউবিজমের সরাসরি প্রভাব কতটা, সে বিষয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু এই জ্যামিতিক বিন্যাসে যে অন্তর্লীন রহস্যময়তা, সেখানেই গগনেন্দ্রনাথ তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনন্য। এরই বিপরীত প্রান্তে রয়েছে কার্টুনের মধ্যে তাঁর প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ। |
|
|
 |
|
|