|
|
|
|
|
|
|
 |
| প্রয়াণের তিন দশক |
| মহানায়ক |
| আমার চারপাশে ঘন অন্ধকার। নিকষ কালো অন্ধকার। আমি দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে আছি একটি আলোকিত বৃত্তের মাঝখানে।’ এ ভাবেই আত্মজীবনী শুরু করেছিলেন তিনি, এই ২৪ জুলাই যাঁর মৃত্যুর তিন দশক পেরোবে। তিনি বাঙালির ‘মহানায়ক’। বাঙালি মানে, আম বাঙালি। কিন্তু যে উত্তমকুমার তারার আলোয় আলোকিত তাঁরই অভিনীত ছবিগুলি ক্রমশ অন্ধকারে চলে যাচ্ছে স্রেফ সংরক্ষণের অভাবে। তাঁর অভিনয়জীবনকে সে ভাবে ধরে রাখতে পারেনি বাঙালি। ফলে আজ যদি কেউ উত্তমকুমারকে পুরো বুঝতে চান, জানতে চান বাংলা সিনেমার ইতিহাসে তাঁর স্থান, তবে উপাদান খুঁজে খুঁজে তাঁকে হয়রান হতে হবে। উত্তমকুমারের সব ছবির রেট্রোস্পেকটিভ দেখানোর স্বপ্ন তো প্রায় অসম্ভব। হারিয়েছে যা তার তালিকা দিতে গেলে আছে যা তাকে ছাপিয়ে চলে যাবে অনেক দূর। |
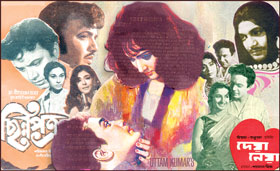 |
| গ্রাফিক্স: বিমল দাস |
প্রযোজকের ঘরেও অনেক ছবি নেই। আর পশ্চিমবঙ্গের মতো আর্দ্র আবহাওয়ার দেশে নেগেটিভ সংরক্ষণের যে মানের পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত সেটা কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগের পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারি উদ্যোগে কিছু কাজ অবশ্য হচ্ছে। চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবনে ছবির প্রিন্ট সংরক্ষণের জন্য যে চারটি চেম্বার আছে তার একটি শুধু উত্তমকুমার অভিনীত ছবির জন্যই নিবেদিত। কিন্তু সেখানে এখনও পর্যন্ত সংরক্ষিত ছবির সংখ্যাটা উত্তমকুমার অভিনীত ছবির মোট সংখ্যার তুলনায় নেহাতই কম, মাত্র ১৪টির মতো, অর্থাৎ পাঁচ শতাংশ। তবে এই ভবনে উত্তম-অভিনীত ছবির শো-কার্ড, তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ইত্যাদি নিয়ে একটি স্থায়ী প্রদর্শনীকক্ষও রয়েছে। কার্যনির্বাহী আধিকারিক জানিয়েছেন, আরও ছবির প্রিন্ট সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। তবে সে কাজ এখন থমকে আছে, ভবনের নতুন উপদেষ্টা কমিটি তৈরি না হওয়ায়। এ দিকে উত্তমকুমারের ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এ মাসের ২৪-২৬ নন্দন ৩-এ নন্দনের আয়োজনে ‘উত্তমকুমার ভিন্ন চোখে’। ‘নায়ক যখন মহানায়ক’ প্রসঙ্গে বলবেন সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য। দেখানো হবে ‘বনপলাশীর পদাবলী’, ‘শঙ্খবেলা’ ও ‘মৌচাক’।
|
| বাংলায় ফেরা |
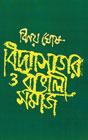 প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়, ১৯৭৩-এ প্রথম বিনয় ঘোষের বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ তিন খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয় তৎকালীন ওরিয়েন্ট লংম্যান থেকে। উনিশ শতকের ইতিহাস ও সমাজের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের বিশ্লেষণ সংবলিত এ-বইয়ের নিবেদন-এ লেখক জানান: ‘ব্যক্তিচরিত্রের সমালোচনার ফলেও কোনো ব্যক্তির ঐতিহাসিক দানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না।’ আঠারো বছর অপ্রকাশের পর ঐতিহাসিক বইটির ওই অখণ্ড সংস্করণ ফের প্রকাশ পেল সম্প্রতি (৪২৫.০০), পাশাপাশি বাংলা প্রকাশনায়ও ফিরল পরিবর্তিত ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান। একই সঙ্গে বেরল আরও একটি বিখ্যাত বাংলা বইয়ের ব্ল্যাকসোয়ান-সংস্করণ, বিষ্ণু প্রভাকরের ‘আওয়ারা মসীহা’র অনুবাদ: ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ (৩২৫.০০)। দেবলীনা ব্যানার্জি কেজ্রিওয়াল অনূদিত এ-বই শরৎচন্দ্রের প্রামাণিক জীবনচরিত, প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বিষ্ণু প্রভাকরের মন্তব্য শরৎচন্দ্র সম্পর্কে: ‘সব সংস্কারের ঊর্ধ্বে চিরদিন চিরব্রাত্য হয়ে কাটিয়ে দিলেন।’ প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়, ১৯৭৩-এ প্রথম বিনয় ঘোষের বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ তিন খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয় তৎকালীন ওরিয়েন্ট লংম্যান থেকে। উনিশ শতকের ইতিহাস ও সমাজের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের বিশ্লেষণ সংবলিত এ-বইয়ের নিবেদন-এ লেখক জানান: ‘ব্যক্তিচরিত্রের সমালোচনার ফলেও কোনো ব্যক্তির ঐতিহাসিক দানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না।’ আঠারো বছর অপ্রকাশের পর ঐতিহাসিক বইটির ওই অখণ্ড সংস্করণ ফের প্রকাশ পেল সম্প্রতি (৪২৫.০০), পাশাপাশি বাংলা প্রকাশনায়ও ফিরল পরিবর্তিত ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান। একই সঙ্গে বেরল আরও একটি বিখ্যাত বাংলা বইয়ের ব্ল্যাকসোয়ান-সংস্করণ, বিষ্ণু প্রভাকরের ‘আওয়ারা মসীহা’র অনুবাদ: ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ (৩২৫.০০)। দেবলীনা ব্যানার্জি কেজ্রিওয়াল অনূদিত এ-বই শরৎচন্দ্রের প্রামাণিক জীবনচরিত, প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বিষ্ণু প্রভাকরের মন্তব্য শরৎচন্দ্র সম্পর্কে: ‘সব সংস্কারের ঊর্ধ্বে চিরদিন চিরব্রাত্য হয়ে কাটিয়ে দিলেন।’
|
| শিল্পীর প্রয়াণ |
 ‘নাইনটিন ফিফটি এইট। জি কে প্রোডাকসনের বিষবৃক্ষ ছবিতে এই গানটা ছিল। প্লেব্যাক নয়, আর্টিস্টের নিজের গলায় গাওয়া।’ বলছেন রমেন মল্লিক, শুনছেন ব্যোমকেশ বক্সী ও অজিত। সত্যজিৎ রায়ের ‘চিড়িয়াখানা’ মনে পড়বে অনেকের। সে ছবিতে ওই গানটা ফিরে ফিরে এসেছে। গানটা লিখেছিলেন সত্যজিৎ নিজেই, সুরও দিয়েছিলেন। আর সেটাই তাঁর নিজের ঢঙে প্রথম নিজের সুর দেওয়া গান। আর গানটা গেয়েছিলেন? নমিতা ঘোষাল। দীর্ঘকাল আড়ালে থাকা এই শিল্পী প্রয়াত হলেন সম্প্রতি। পারিবারিক সূত্রেই সঙ্গীতের তালিম। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন দেবব্রত বিশ্বাস, সন্তোষ সেনগুপ্তের কাছে। রেকর্ডও প্রকাশিত হয় কয়েকটি। ‘চিড়িয়াখানা’ ছাড়া গেয়েছেন নিত্যানন্দ দত্তের ‘বাক্সবদল’ ছবিতে। সঙ্গীতচর্চার সঙ্গী ছিলেন তাঁর ভাই, সঙ্গীতশিল্পী অনুপ ঘোষাল। ‘নাইনটিন ফিফটি এইট। জি কে প্রোডাকসনের বিষবৃক্ষ ছবিতে এই গানটা ছিল। প্লেব্যাক নয়, আর্টিস্টের নিজের গলায় গাওয়া।’ বলছেন রমেন মল্লিক, শুনছেন ব্যোমকেশ বক্সী ও অজিত। সত্যজিৎ রায়ের ‘চিড়িয়াখানা’ মনে পড়বে অনেকের। সে ছবিতে ওই গানটা ফিরে ফিরে এসেছে। গানটা লিখেছিলেন সত্যজিৎ নিজেই, সুরও দিয়েছিলেন। আর সেটাই তাঁর নিজের ঢঙে প্রথম নিজের সুর দেওয়া গান। আর গানটা গেয়েছিলেন? নমিতা ঘোষাল। দীর্ঘকাল আড়ালে থাকা এই শিল্পী প্রয়াত হলেন সম্প্রতি। পারিবারিক সূত্রেই সঙ্গীতের তালিম। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন দেবব্রত বিশ্বাস, সন্তোষ সেনগুপ্তের কাছে। রেকর্ডও প্রকাশিত হয় কয়েকটি। ‘চিড়িয়াখানা’ ছাড়া গেয়েছেন নিত্যানন্দ দত্তের ‘বাক্সবদল’ ছবিতে। সঙ্গীতচর্চার সঙ্গী ছিলেন তাঁর ভাই, সঙ্গীতশিল্পী অনুপ ঘোষাল।
|
| তর্কপ্রবণ |
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ‘এমন একজন লেখক যার সঙ্গে তর্ক করা চলে’ এমনটাই লেখা আছে তাঁর নতুন গদ্যের বই পাতালের চিরকুট-এর (সন্দর্ভ প্রকাশ, ১২৫.০০) ব্লার্বে। বিষয় যেমন বিবিধ, তেমনই তর্কপ্রবণ প্রতিটি নিবন্ধ। আবার বাক্যের ফাঁকফোকর দিয়ে ডালপালা ছড়ায় জরুরি কিছু প্রসঙ্গ: ‘‘যদি শুধু উদ্বাস্তু সমস্যার কথা বলা হত, যদি শুধু সীমান্ত আলাদা হয়ে যাওয়ার গল্প হত, ‘মেঘে ঢাকা তারা’ আজ ফুরিয়ে যেত। আজ টালিগঞ্জে কোথাও গল্পে পড়া বাস্তুহারা কলোনির রেশ নেই।... অথচ নীতা আজও করুণ চোখে চেয়ে থাকে।’’ বই থেকে বেরিয়ে প্রায় এমনই বিষয় নিয়ে বলবেনও তিনি, ২০ জুলাই বুধবার সন্ধে ছ’টায় নন্দন-৩-এ, অলোকচন্দ্র চন্দ্র স্মৃতি-বক্তৃতা ‘বাঙালির আধুনিকতা: বাঙালির ছায়াছবি’। উদ্যোগে সিনে সেন্ট্রাল।
|
| গ্রন্থাগার ১৭৫ |
বেসরকারি উদ্যোগে ১৮৩৬-এর ২১ মার্চ এসপ্ল্যানেড রো ইস্ট-এ এফ পি স্ট্রং-এর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি। সেখানে যে কেউ বই পড়তে আসতে পারতেন। ১৮৯১-এ একাধিক সরকারি সচিবালয়ের গ্রন্থাগারকে একত্র করে গঠিত হয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ১৯০৩-এর ৩০ জানুয়ারি মেটকাফ হলে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত করে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সংযুক্ত লাইব্রেরিটি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি নামেই পরিচিত হয়। সেই সময় থেকে এটি সরকারি গ্রন্থাগার। বই, পত্রপত্রিকার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯২৩-এ লাইব্রেরিকে নিয়ে আসা হয় ৫ এসপ্ল্যানেড ইস্ট-এ বিদেশ ও সামরিক সচিবালয়ের বাড়িতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কিছুকাল লাইব্রেরির অস্থায়ী ঠিকানা হয় জবাকুসুম হাউস। স্বাধীনতার পরে এটিই হল জাতীয় গ্রন্থাগার, প্রথম গ্রন্থাগারিক বি এস কেশবন। সেই সময়েই গ্রন্থাগার উঠে এল বেলভিডিয়ার হাউসে। এ বছর ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার ১৭৫ বছর উপলক্ষে ১৬ জুলাই ভাষা ভবনের কনফারেন্স হল-এ প্রথম ‘বি এস কেশবন বক্তৃতা’-য় ‘কালচার্স অব কপিরাইট: অথর্স অ্যান্ড পাবলিশার্স ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া’ বিষয়ে বললেন এ আর বেঙ্কটচলপথি। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সচিব জহর সরকার।
|
| খানা-বাড়ি |
বাদলদিনে মন যদি ম্যাজিক-পানে ধায়, চিন্তা নেই, শহরে আছেন পি সি সরকার (জুনিয়র)! শহরে তাঁর জাদুর খেলা শুরু হয়েছে সদ্য, আর শহর ছাড়িয়ে, একটুখানি গেলেই আছে অন্য একটি জিনিস। ‘টাওয়ার ঘোস্ট রেস্টুরেন্ট: নীলকুঠি’! হানাবাড়ি অনেকেই দেখেছেন, কিন্তু ‘খানা-বাড়ি’! যেখানে ভুতুড়ে ম্যাজিক-এ টেবিলে চলে আসবে জিভে-জল আনা সব খাদ্য! ‘মূল ভাবনাটা পি সি সরকারের, শুনেই ভাবলাম যে এই ম্যাজিকটা সত্যি করতে হবে! পৃথিবীতে এ জিনিস আর নেই!’ জানাচ্ছেন টাওয়ার গ্রুপ-এর সিএমডি রামেন্দু চট্টোপাধ্যায়। উলুবেড়িয়ার কাছেই কুলেশ্বরে এই বিচিত্র ভূত-ভোজনের আয়োজন। উৎসাহীরা চোখে দেখুন, চেখে দেখুন, এমনটাই চাইছে এই নয়া ‘নীলকুঠি’!
|
| ষাটে সন্দীপ |
 সত্তরের দশকের গোড়ার কথা। লিটল ম্যাগাজিনের খোঁজ করতে গিয়ে বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে প্রায় শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র সন্দীপ দত্তকে। হতাশ সন্দীপ স্থির করলেন, নিজেই গড়ে তুলবেন ছোট পত্রিকার ভাণ্ডার। হাত খরচের টাকা জমিয়ে কেনা কিছু পত্রিকা নিয়ে ২৩ জুন ১৯৭৮-এ ১৮ এম টেমার লেনে নিজের বসত বাড়ির একতলায় প্রতিষ্ঠা করলেন লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র। এত বছর ধরে এই লাইব্রেরি শুধু গুদাম হয়েই থাকেনি, লিটল ম্যাগাজিনকে জনপ্রিয় করবার জন্য সন্দীপের উদ্যোগে প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, পত্রিকা প্রকাশ সবই হয়ে চলেছে ওই লাইব্রেরি থেকে। আদ্যন্ত লিটল ম্যাগাজিনপ্রেমী সেই মানুষটি পূর্ণ করলেন ষাট বছর। এই উপলক্ষে লিটল ম্যাগাজিন পাঠচক্রের উদ্যোগে ২৪ জুলাই, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টায় বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে থিয়জফিক্যাল সোসাইটি হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বহু বিশিষ্টজন উপস্থিত থাকবেন। সত্তরের দশকের গোড়ার কথা। লিটল ম্যাগাজিনের খোঁজ করতে গিয়ে বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে প্রায় শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র সন্দীপ দত্তকে। হতাশ সন্দীপ স্থির করলেন, নিজেই গড়ে তুলবেন ছোট পত্রিকার ভাণ্ডার। হাত খরচের টাকা জমিয়ে কেনা কিছু পত্রিকা নিয়ে ২৩ জুন ১৯৭৮-এ ১৮ এম টেমার লেনে নিজের বসত বাড়ির একতলায় প্রতিষ্ঠা করলেন লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র। এত বছর ধরে এই লাইব্রেরি শুধু গুদাম হয়েই থাকেনি, লিটল ম্যাগাজিনকে জনপ্রিয় করবার জন্য সন্দীপের উদ্যোগে প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, পত্রিকা প্রকাশ সবই হয়ে চলেছে ওই লাইব্রেরি থেকে। আদ্যন্ত লিটল ম্যাগাজিনপ্রেমী সেই মানুষটি পূর্ণ করলেন ষাট বছর। এই উপলক্ষে লিটল ম্যাগাজিন পাঠচক্রের উদ্যোগে ২৪ জুলাই, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টায় বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে থিয়জফিক্যাল সোসাইটি হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বহু বিশিষ্টজন উপস্থিত থাকবেন।
|
| মানবিক |
আইআইটি-তে পড়াশোনা করার সময়েই সংকল্প করেন অশোককুমার, সহপাঠীদের মতো বিদেশ যাবেন না, দেশসেবা করবেন। এমন একটা চাকরি করতে চেয়েছিলেন, যেখানে সাধারণের সমস্যার সমাধান করা যায়, তাঁদের জন্যে কাজ করা যায়। আইপিএস অফিসার হওয়ার পর এখন পর্যন্ত সে রকম সেবাতেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন অশোককুমার, সে জন্যে জাতীয়-আন্তর্জাতিক স্তরে পুরস্কৃতও হয়েছেন। নিজের সেই কর্মকাণ্ড নিয়ে বইও লিখে ফেলেছেন খাকির পেছনে মানুষ (ডায়মন্ড বুকস, ১২৫.০০), সঙ্গে সহ-লেখক লোকেশ ওহরি। বইটি পড়ে কিরণ বেদী-র মনে হয়েছে: পুলিশের কাজকর্ম নিয়ে যে বিশ্বাসযোগ্যতা কমে আসছিল, এ-বই তা ফিরিয়ে আনবে, পুলিশের ভিতর মনুষ্যত্বের দিকটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবে। ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশ পেয়েছে বইটির: হিউম্যান ইন খাকি (ডায়মন্ড বুকস, ১৪০.০০)।
|
| আচার্য-স্মৃতি |
 দুই আলেকজান্ডার। প্রথমজন পেডলার আর দ্বিতীয় ব্রাউন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের রসায়নবিজ্ঞানী হয়ে ওঠার পেছনে এঁদের দু’জনেরই প্রভাব রয়েছে। তবে বিজ্ঞানীর থেকে প্রফুল্লচন্দ্রের সমাজসেবী সত্তাকে আলাদা করা অসম্ভব। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর তিনি ছিলেন সভাপতি, অতএব যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্যের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে ছিল দু’দিনের আলোচনাচক্র। রসায়ন বিভাগের উদ্যোগে ৮ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হল শ্বেতপাথরের একটি আবক্ষ মূর্তি, শিল্পী গোপাল মিস্ত্রী (সঙ্গে গোপী দে সরকারের ছবিতে)। ত্রিগুণা সেন সভাগৃহে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ দেন অশোককুমার মল্লিক। এর পর স্লাইড সহ প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন ও কাজকে তুলে ধরেন অনিমেষ চক্রবর্তী। আলোচনায় ছিলেন মুম্বই, কানপুর আই আই টি, ভুবনেশ্বর, বেঙ্গালুরু, তেজপুর এবং বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ও অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত প্রায় ২৫০ গবেষক-রসায়নবিদ। এ বছরটি আন্তর্জাতিক রসায়নবর্ষ। জানা গেল, ‘ইন্ডিয়ান জার্নাল অব কেমিস্ট্রি’ থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সমস্ত কাজ নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত হবে। দুই আলেকজান্ডার। প্রথমজন পেডলার আর দ্বিতীয় ব্রাউন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের রসায়নবিজ্ঞানী হয়ে ওঠার পেছনে এঁদের দু’জনেরই প্রভাব রয়েছে। তবে বিজ্ঞানীর থেকে প্রফুল্লচন্দ্রের সমাজসেবী সত্তাকে আলাদা করা অসম্ভব। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর তিনি ছিলেন সভাপতি, অতএব যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্যের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে ছিল দু’দিনের আলোচনাচক্র। রসায়ন বিভাগের উদ্যোগে ৮ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হল শ্বেতপাথরের একটি আবক্ষ মূর্তি, শিল্পী গোপাল মিস্ত্রী (সঙ্গে গোপী দে সরকারের ছবিতে)। ত্রিগুণা সেন সভাগৃহে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ দেন অশোককুমার মল্লিক। এর পর স্লাইড সহ প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন ও কাজকে তুলে ধরেন অনিমেষ চক্রবর্তী। আলোচনায় ছিলেন মুম্বই, কানপুর আই আই টি, ভুবনেশ্বর, বেঙ্গালুরু, তেজপুর এবং বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ও অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত প্রায় ২৫০ গবেষক-রসায়নবিদ। এ বছরটি আন্তর্জাতিক রসায়নবর্ষ। জানা গেল, ‘ইন্ডিয়ান জার্নাল অব কেমিস্ট্রি’ থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সমস্ত কাজ নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত হবে।
|
| তিন দশক |
শুরু থেকেই সিনেমা বাঁধা পড়েছে সেলুলয়েডে, কিন্তু থিয়েটার? শুধু স্মৃতিতে, আর নগণ্য সংখ্যক স্থিরচিত্রে। থিয়েটার সংক্রান্ত তথ্য-ছবি সংরক্ষণ করে রাখা যে কত জরুরি, ১৯৭৪-এই সে কথা ভেবেছিলেন প্রতিভা অগ্রবাল, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় আর খালেদ চৌধুরী। শেষে বি ডি সুরেকা আর ইয়ামা শ্রফকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা ১৯৮১-র ১৯ জুলাই সূচনা করলেন ‘নাট্য শোধ সংস্থান’-এর। ১১ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট থেকে ৪ লি রোড হয়ে সল্ট লেকে নিজস্ব নাট্য ভবন-এ স্থিতু এই প্রতিষ্ঠান পেরিয়ে এল ত্রিশ বছর। গত শনিবার সেই উপলক্ষে ওদের বিপুল সংগ্রহ থেকে নাট্য ভবনেই এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন গিরিশ কারনাড, ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সচিব জহর সরকার। রবিবার ও আজ সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় ভারতে থিয়েটার আর্কাইভিং-এর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা, থাকছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রদর্শনী ২২ পর্যন্ত।
|
| গোপনচারী |
সরকারি অনুদান ভরসা, পাশাপাশি শিরোধার্য মহাকরণের লাল ফিতে। এর মধ্যেও এ শহরের যে কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কিছু ‘কাজ’ করে উঠতে পেরেছে, তার মধ্যে সব থেকে গোপনচারী বোধহয় সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া। প্রত্নতত্ত্ব খায় না মাথায় দেয়, তা নিয়ে কারই বা মাথাব্যথা? কিন্তু এখন প্রত্নতত্ত্ব শুধু যে মাটি খোঁড়াখুঁড়ির বৃত্তান্ত নয়, তার বাইরেও অনেক কিছু, জ্ঞানচর্চার নানা শাখার সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করে খোলা সম্ভব অতীত উদ্ধারের দিকদিগন্ত, একত্র করা সম্ভব দেশ-বিদেশের পণ্ডিতদেরও, বারবার তা দেখিয়ে দিয়েছে এই কেন্দ্রের তরুণ তুর্কিরা। প্রকাশিত হয়েছে অজস্র মূল্যবান বইপত্র। ‘প্রত্নসমীক্ষা’ নামে তাদের জার্নালের যে সংখ্যাটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক মানের। নানা গবেষণা-প্রকল্পে কাজ চলছে কেন্দ্রীয় সহায়তায়। এই প্রতিষ্ঠানটির বোধহয় আর একটু মর্যাদা প্রাপ্য।
|
| চুপকথা |
 |
| দশে থাকে দিক, সুতরাং দশটি তুমুল সফল অ্যালবাম পেরিয়ে তিনি, শিলাজিৎ, নতুন দিশার সন্ধানে যাত্রা করেন যদি, বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। দীপঙ্কর-শৌভিকের ‘চুপকথা’ ছবিতে তিনি মুখ্য চরিত্রাভিনেতা। ছবিতে অভিনয় আগেও করেছেন, প্রশংসা পেয়েছেন, কিন্তু এমন মুখ্য চরিত্রে খুব বেশি নয়। অবশ্য, তাঁকে উত্তেজিত করছে অন্য একটি দায়িত্ব। সঙ্গীত পরিচালক। এই ছবির গান এবং আবহ রচনার দায়িত্বেও তিনি। ‘ভাবলাম চ্যালেঞ্জটা নিয়েই দেখি’, হাসছেন গায়ক-নায়ক। এ বার তিনি নিজের সঙ্গে খেলছেন, এতদিন সুর করতেন মূলত নিজের কণ্ঠটি ভেবে, এ বার গল্পের দাবিতে, অন্যের গলা ভেবে তৈরি হচ্ছে গান। যে শিল্পী-তালিকাটি বেছেছেন, তা-ও অভিনব। জয় সরকার, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, কমলিকা, রাধিকা, অনন্যা, শ্রীজাত...। গান তৈরির কাহিনিটিও আশ্চর্য। একই ‘ব্রিফিং’-এ তিনি ছাড়াও গান লিখেছেন তিন নবীন গীতিকার, প্রসেনজিৎ, কিংশুক এবং দীপাংশু। তারপর কার গান কী ভাবে কোথায় থাকবে, সে সব এখনই ভাঙছেন না সঙ্গীত পরিচালক। ‘গাইছেন না? ‘কী জানি...’, শিলাজিতের গলায় রহস্য, ‘ছবিতে আরও একজনের লেখা গান আছে, জানেন, সুরেন দাস ঠাকুর!’ কে তিনি? ‘নতুন এক পুরাতনী’! মানে? গিটারটি কাঁধে শিলাজিৎ উদাস ভাবে আকাশপানে তাকালেন... |
|
|
| |
| কাজপাগল |
| কর্মজীবনের শুরুতে বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করতে গিয়ে দেশ-বিদেশের চিঠিতে সাঁটানো ডাকটিকিটে আকৃষ্ট হন তিনি। সেই সূত্র ধরে ডাকটিকিটের জগতে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন শিল্পী দীপক দে। চট্টগ্রামের মুরাদপুরে জন্ম ১৯৩৮-এর ১৮ জুন। বাবার চাকরিসূত্রে রেঙ্গুনে বাস, ১৯৪৫-এ ফিরে চট্টগ্রামের জোরারগঞ্জে স্কুলে ভর্তি হন। দেশ বিভাগের পর শালকিয়াতে, দু’বছর পর ত্রিপুরায়। ১৯৫৭-য় মাধ্যমিক। এ বছরই কলকাতা ফিরে মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ভর্তি হন। শেষমেশ ১৯৬০-এ ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে। ১৯৬৫-তে কর্মজীবন শুরু বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে। চলছিল শিল্পের সঙ্গে সাহিত্যচর্চা। |
 ১৯৭২-এ জড়িয়ে পড়েন মুর্শিদাবাদে সারা বাংলা কবি সম্মেলনের আয়োজনে। দু’বছর পর সম্পাদনা করেন প্রথম বাংলা লিটল ম্যাগাজিন ‘ডাইরেক্টরি’। কলকাতায় সাঁওতালি এবং দার্জিলিঙে নেপালি কবি সম্মেলন-এর আয়োজন করেন। ১৯৮৩-তে রাষ্ট্রপুঞ্জের এক প্রতিযোগিতায় দীপকবাবু একখানি ডাকটিকিটের নকশা করে পাঠান। ‘চাইল্ড সারভাইভাল’ শীর্ষকে সারা বিশ্ব থেকে চারটি নকশা পুরস্কৃত হয়। প্রথম ভারতীয় হিসেবে দীপকবাবুর নকশা স্বীকৃত হয়। এর পর একে একে সত্যজিৎ রায়, মেঘনাদ সাহা, কলকাতা ৩০০; চলল ডাক টিকিটের নকশা এবং ফার্স্ট-ডে কভারেরও। ওঁর ঝুলিতে এখন প্রায় ৫০টিরও বেশি কভার নকশার শিরোপা আছে, সঙ্গে নিজের সংগ্রহের অজস্র মূল্যবান ডাকটিকিট। ১৯৯০-তে আয়োজন করেন সিনেমা ইত্যাদি নিয়ে ডাক-প্রদর্শনী সিনেপেক্স। সিনেমা ও মুদ্রণচর্চা নিয়ে ওঁর ডাকটিকিট সংগ্রহ বিশ্বের বৃহত্তম। দু’খানা বই লিখেছেন শ্রী একটি রাগের নাম এবং রাগ মালকোষ শীর্ষকে। সম্পাদনা করেছেন ‘ফিল্মিং’ ও ‘দ্য স্ট্যাম্পস ওয়ার্ল্ড’ পত্রিকা। ১৯৭৯-এ কলকাতা জিপিও-তে ডাক জাদুঘর গড়ে ওঠার সময় তিনি সক্রিয় ছিলেন। উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন ভারতীয় ডাকটিকিট সংস্থায়। সত্তর পেরিয়েও তিনি কাজপাগল। ১৯৭২-এ জড়িয়ে পড়েন মুর্শিদাবাদে সারা বাংলা কবি সম্মেলনের আয়োজনে। দু’বছর পর সম্পাদনা করেন প্রথম বাংলা লিটল ম্যাগাজিন ‘ডাইরেক্টরি’। কলকাতায় সাঁওতালি এবং দার্জিলিঙে নেপালি কবি সম্মেলন-এর আয়োজন করেন। ১৯৮৩-তে রাষ্ট্রপুঞ্জের এক প্রতিযোগিতায় দীপকবাবু একখানি ডাকটিকিটের নকশা করে পাঠান। ‘চাইল্ড সারভাইভাল’ শীর্ষকে সারা বিশ্ব থেকে চারটি নকশা পুরস্কৃত হয়। প্রথম ভারতীয় হিসেবে দীপকবাবুর নকশা স্বীকৃত হয়। এর পর একে একে সত্যজিৎ রায়, মেঘনাদ সাহা, কলকাতা ৩০০; চলল ডাক টিকিটের নকশা এবং ফার্স্ট-ডে কভারেরও। ওঁর ঝুলিতে এখন প্রায় ৫০টিরও বেশি কভার নকশার শিরোপা আছে, সঙ্গে নিজের সংগ্রহের অজস্র মূল্যবান ডাকটিকিট। ১৯৯০-তে আয়োজন করেন সিনেমা ইত্যাদি নিয়ে ডাক-প্রদর্শনী সিনেপেক্স। সিনেমা ও মুদ্রণচর্চা নিয়ে ওঁর ডাকটিকিট সংগ্রহ বিশ্বের বৃহত্তম। দু’খানা বই লিখেছেন শ্রী একটি রাগের নাম এবং রাগ মালকোষ শীর্ষকে। সম্পাদনা করেছেন ‘ফিল্মিং’ ও ‘দ্য স্ট্যাম্পস ওয়ার্ল্ড’ পত্রিকা। ১৯৭৯-এ কলকাতা জিপিও-তে ডাক জাদুঘর গড়ে ওঠার সময় তিনি সক্রিয় ছিলেন। উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন ভারতীয় ডাকটিকিট সংস্থায়। সত্তর পেরিয়েও তিনি কাজপাগল। |
|
|
|
|
 |
|
|