|
|
|
|
|
|
|
 |
| নগর-কেন্দ্রে ঐতিহ্যবাহী ভবন |
| বিধানসভা পঁচাত্তরে |
বাংলায় আইনপরিষদের কাজ শুরু ১৮৬২ থেকে, লেফটেন্যান্ট গভর্নর ও কয়েকজন মনোনীত সদস্য নিয়ে। আস্তে আস্তে নির্বাচিত সদস্যরা  এসেছেন। সভা বসত বেলভেডিয়ারের লাটপ্রাসাদে বা টাউন হলে। এক সময় শহরের কেন্দ্রে, গঙ্গার কাছেই সুবিশাল অঞ্চল জুড়ে পরিকল্পিত হল আইনসভার নিজস্ব ভবন। ১৯৩৫ সালে ‘ভারত শাসন আইন’-এর বলে ১৯৩৭ সালের ৯ এপ্রিল চালু হল ‘বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা’-র কার্যক্রম। গঠিত হল ‘বিধানসভা’ ও ‘বিধান পরিষদ’। আজিজুল হক বিধানসভার প্রথম স্পিকার ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বিধান পরিষদে প্রথম সভাপতি। এসেছেন। সভা বসত বেলভেডিয়ারের লাটপ্রাসাদে বা টাউন হলে। এক সময় শহরের কেন্দ্রে, গঙ্গার কাছেই সুবিশাল অঞ্চল জুড়ে পরিকল্পিত হল আইনসভার নিজস্ব ভবন। ১৯৩৫ সালে ‘ভারত শাসন আইন’-এর বলে ১৯৩৭ সালের ৯ এপ্রিল চালু হল ‘বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা’-র কার্যক্রম। গঠিত হল ‘বিধানসভা’ ও ‘বিধান পরিষদ’। আজিজুল হক বিধানসভার প্রথম স্পিকার ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বিধান পরিষদে প্রথম সভাপতি।
তেত্রিশ বিঘা জমির উপর ১৯২৮ সালে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল বিধানসভা ভবনের। জে গ্রিভস এই বিশাল ভবনটির মুখ্য স্থপতির দায়িত্ব পালন করেন। |
 |
বাড়ি তৈরি হতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল। বাড়িটি তৈরি করে মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি, খরচ হয়েছিল ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। বাড়িটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্থাপত্যশৈলীর মিশ্রণে তৈরি। ভারতীয় ইসলামি স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের নমুনা। ১৯৩৭ থেকে আজ পর্যন্ত ৭৫ বছর ধরে ভবনটি শহরের ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র। বিশাল বাগানের মধ্যে মূল বাড়ি-সহ ছোট-বড় আরও চারটি বাড়ি আছে, যার মোট আয়তন প্রায় ৭৩০০ বর্গমিটার। মূল বাড়িতে ছোট-বড় ১৫০টি ঘর আছে। বিধানসভার গ্রন্থাগার ও লেখ্যাগার খুবই উল্লেখযোগ্য। গম্বুজাকৃতি ছাদে ঢাকা বিধানসভা কক্ষে ২৯৪ জন সদস্যের আসন আছে। লবির দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে শিল্পী অতুল বসু ও অন্যদের আঁকা মনীষীদের তৈলচিত্র। ৪-৬ ডিসেম্বর এখানেই অনুষ্ঠিত হবে ৭৫ বর্ষপূর্তি উত্সব। থাকবেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, লোকসভার স্পিকার মীরা কুমার, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী-সহ বহু বিশিষ্ট জন। প্রকাশ পাবে স্মারকগ্রন্থও। সঙ্গে বিধানসভা ভবন ও বিধানসভার প্রতীকচিহ্নের ছবি।
|
| যৌবনবাউল |
 ‘কবিতা থেকে কবিতার সঞ্চার পথে পুনরুক্তিপ্রবণতার যথাসাধ্য খারিজ হতে দেখলেই খুশি হই। আমার বিশ্বাস..., সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে পারম্পর্য বলে কিছু আছে।’ ১৯৫৯-এর সেই ‘যৌবনবাউল’ কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর কবিতায়ও এই বিশ্বাস বজায় রেখেছেন। কবিতা, ছড়া, গল্প, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ, নাট্যকোলাজ যে দিকেই যান তিনি, পরিবর্তনের পরম্পরা তাঁকে চিরতরুণ করে রাখে। আশিতে এসেও তাই ‘যৌবনবাউল’ তিনি। শান্তিনিকেতনে পড়তে পড়তেই অমর্ত্য সেন আর মধুসূদন কুণ্ডুকে নিয়ে ‘স্ফুলিঙ্গ’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। আদর্শ ছিল প্লেখানভ আর মার্টভের সঙ্গে লেনিনের পত্রিকা ‘ইসক্রা’। তার পরে কলকাতা, বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনা। তার পরে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত পার করে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্বের অধ্যাপনা। অলোকরঞ্জনের আশি বছর উপলক্ষে ‘অহর্নিশ’ পত্রিকার (সম্পা: শুভাশিস চক্রবর্তী) বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবেন শঙ্খ ঘোষ, ৩ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দুমতী সভাঘরে। আশ্চর্য সব চিঠিপত্র, বন্ধুত্বকথা, গুরুদক্ষিণা, অলোকরঞ্জনকে নিয়ে নতুন-পুরনো আলোচনা, জীবনপঞ্জি, শব্দকোষ, ছবি নিয়ে বিপুলায়তন সংখ্যাটি বর্ণময় এই বিশ্বনাগরিকের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য। ‘কবিতা থেকে কবিতার সঞ্চার পথে পুনরুক্তিপ্রবণতার যথাসাধ্য খারিজ হতে দেখলেই খুশি হই। আমার বিশ্বাস..., সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে পারম্পর্য বলে কিছু আছে।’ ১৯৫৯-এর সেই ‘যৌবনবাউল’ কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর কবিতায়ও এই বিশ্বাস বজায় রেখেছেন। কবিতা, ছড়া, গল্প, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ, নাট্যকোলাজ যে দিকেই যান তিনি, পরিবর্তনের পরম্পরা তাঁকে চিরতরুণ করে রাখে। আশিতে এসেও তাই ‘যৌবনবাউল’ তিনি। শান্তিনিকেতনে পড়তে পড়তেই অমর্ত্য সেন আর মধুসূদন কুণ্ডুকে নিয়ে ‘স্ফুলিঙ্গ’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। আদর্শ ছিল প্লেখানভ আর মার্টভের সঙ্গে লেনিনের পত্রিকা ‘ইসক্রা’। তার পরে কলকাতা, বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনা। তার পরে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত পার করে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্বের অধ্যাপনা। অলোকরঞ্জনের আশি বছর উপলক্ষে ‘অহর্নিশ’ পত্রিকার (সম্পা: শুভাশিস চক্রবর্তী) বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবেন শঙ্খ ঘোষ, ৩ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দুমতী সভাঘরে। আশ্চর্য সব চিঠিপত্র, বন্ধুত্বকথা, গুরুদক্ষিণা, অলোকরঞ্জনকে নিয়ে নতুন-পুরনো আলোচনা, জীবনপঞ্জি, শব্দকোষ, ছবি নিয়ে বিপুলায়তন সংখ্যাটি বর্ণময় এই বিশ্বনাগরিকের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য।
|
| অতিথি |
 ছোটবেলায় বাবার গলায় প্রচলিত লোকগান শুনে আগ্রহ তৈরি হয় বার্লিনের পিটার পাঙ্কের। পরে ঠিক করলেন, ‘ধ্রুপদ’ শিখতে হবে। লোকগায়ক ‘ট্রুবাডুর’-দের গানও তাঁকে প্রভাবিত করে। ’৭৩-এ গান শেখার জন্য এসে ভর্তি হন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। গানের সন্ধানে ঘুরেছেন ভারতের নানা স্থানে। তালিম নিয়েছেন ওস্তাদদের কাছে। তুর্কি সিরিয়ার প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের নিয়ে গড়েছেন ‘ট্রুবাডুরস ইউনাইটেড’। অনুষ্ঠান করেছেন রেডিয়ো বার্লিনে, প্রকাশ পেয়েছে অজস্র সিডি। লিখেছেন ইন্ডিয়া: আ ফেস্টিভ্যাল অব কালাসর্ বা ড্রিমটকার। সম্প্রতি ম্যাক্সমুলার ভবনে তাঁর নতুন বই সিংগারস ডাই টোয়াইস (সিগাল)-এর প্রকাশ উপলক্ষে ঘুরে গেলেন এ শহরে। পিটারের জীবন, সংগীত সাধনা নিয়ে জমে উঠল আলাপ। আলোচক ছিলেন প্রয়াত পণ্ডিত রাধিকামোহন মৈত্রেয়র সুযোগ্য ছাত্র সোমজিত্ দাশগুপ্ত। ছোটবেলায় বাবার গলায় প্রচলিত লোকগান শুনে আগ্রহ তৈরি হয় বার্লিনের পিটার পাঙ্কের। পরে ঠিক করলেন, ‘ধ্রুপদ’ শিখতে হবে। লোকগায়ক ‘ট্রুবাডুর’-দের গানও তাঁকে প্রভাবিত করে। ’৭৩-এ গান শেখার জন্য এসে ভর্তি হন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। গানের সন্ধানে ঘুরেছেন ভারতের নানা স্থানে। তালিম নিয়েছেন ওস্তাদদের কাছে। তুর্কি সিরিয়ার প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের নিয়ে গড়েছেন ‘ট্রুবাডুরস ইউনাইটেড’। অনুষ্ঠান করেছেন রেডিয়ো বার্লিনে, প্রকাশ পেয়েছে অজস্র সিডি। লিখেছেন ইন্ডিয়া: আ ফেস্টিভ্যাল অব কালাসর্ বা ড্রিমটকার। সম্প্রতি ম্যাক্সমুলার ভবনে তাঁর নতুন বই সিংগারস ডাই টোয়াইস (সিগাল)-এর প্রকাশ উপলক্ষে ঘুরে গেলেন এ শহরে। পিটারের জীবন, সংগীত সাধনা নিয়ে জমে উঠল আলাপ। আলোচক ছিলেন প্রয়াত পণ্ডিত রাধিকামোহন মৈত্রেয়র সুযোগ্য ছাত্র সোমজিত্ দাশগুপ্ত।
|
| অমল সিনড্রোম |
রবীন্দ্রনাটকের নতুন মঞ্চায়ন তো অনেক হল, কিন্তু এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে ভেঙে গড়া? না, শহরের মঞ্চে তেমন কাজ হাতেগোনাও নয়। তারই মধ্যে অধ্যাপক অমল সেন সম্প্রতি এলেন অ্যাকাডেমির মঞ্চে। শুধু তিনি নন, আসলে মঞ্চে এল ‘অমল সিনড্রোম’, ‘সংলাপ কলকাতা’র নতুন নাটক। ক্রমশ একা হতে হতে অমল রবীন্দ্রনাথকেই আঁকড়ে ধরেন। তাঁর চোখে ভাসতে থাকে দইওয়ালা নান্টু, বলাই। রীতিমতো চিকিত্সায় উদ্যোগী হয় তার পরিবার। সেখানে হঠাত্ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। নতুন করে ডাকঘরের প্রভাবে এই নাটকের নির্দেশক কুন্তল মুখোপাধ্যায় বলছেন, “আসলে সকলে প্রত্যেকে একা আমরা। সেই একাকীত্বে রবীন্দ্রনাথ কী করে ঢুকে পড়েন তারই একটা ফ্যান্টাসি-র রূপ নাটকটা।” নাটকটির দ্বিতীয় অভিনয় ৫ ডিসেম্বর গিরিশ মঞ্চে।
|
| ভারতের বিলে |
‘বাল্মিকী প্রতিভা’-র মঞ্চাভিনয় কারাবন্দিদের জীবন কী ভাবে পালটে দিল, তার প্রমাণ এ শহরেরই বুকে বানানো ছবি ‘মুক্তধারা’। এ বার বন্দিরা নাটকে তুলে ধরবেন স্বামী বিবেকানন্দের জীবন। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ এবং রাজ্য সংশোধনী পরিষেবা দফতর-এর যৌথ উদ্যোগে আলিপুর কেন্দ্রীয় ও প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের ৩৪ জন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পুরুষ বন্দি অভিনয় করবেন ‘ভারতের বিলে’ নাটকে। কলকাতারই সাংস্কৃতিক সংস্থা ‘মারু বেহাগ’ এটি মঞ্চস্থ করছে রবীন্দ্র সদনে, ৪ ডিসেম্বর সন্ধেয়। নির্দেশনায় জলি গুহরায়। ‘থিয়েটারে লোকশিক্ষে হয়’ শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই তাঁদের অনুপ্রেরণা। রাজ্যের সব সংশোধনাগারেই বন্দিদের নিয়ে এই ধরনের কাজ চলছে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ওদের জীবনেও আশা ফুটছে, বলছিলেন সারদাপীঠ-এর সচিব স্বামী দিব্যানন্দ।
|
| সিনেমার মঞ্চগান |
২০ নভেম্বর ১৮৯৭। ক্লাসিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল ‘আলিবাবা’। প্রযোজক-পরিচালক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। আবদাল্লা-মর্জিনার গান ‘আয় বাঁদি তুই বেগম হবি, খোয়াব দেখেছি’তে নতুন স্বপ্ন দেখল দর্শক। অমরেন্দ্র-বান্ধব হীরালাল সেনের ক্যামেরায় ১৮৯৮ থেকে টুকরো দৃশ্য চিত্রায়িত হলেও ১৯০৪-এ প্রদর্শিত হল ‘আলিবাবা’-র পূর্ণরূপ। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এ বিজ্ঞাপিত হল ‘Alibaba./ complete drama! Vivid drama! Flawless drama!/...Sequences will come from the Royal Box.’। নির্বাক যুগে সিনেমার সঙ্গে বাজত মঞ্চগানের সুর। অথচ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ‘শতবর্ষ’ উদযাপনের আড়ম্বরে কোথাও স্থান পায়নি পূর্বসূরি অমরেন্দ্রনাথ-হীরালালদের কৃতিত্ব। তাঁদের স্মরণে রেখে, মঞ্চ ও সিনেমার মেলবন্ধনে অ্যাকাডেমি থিয়েটারের উদ্যোগ ‘সিনেমার মঞ্চগান’ ৬-৭ ডিসেম্বর, সন্ধে সাড়ে ৬টায়, অ্যাকাডেমি-তে। গানে দেবজিত্ এবং ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা যাবে উত্তমকুমারের মঞ্চ ও জীবনের চিত্রপ্রদর্শনী ‘নায়ক’, প্রকাশিত হবে গিরিশ থেকে শম্ভু মিত্র পর্ব নিয়ে চিত্তরঞ্জন ঘোষের মঞ্চরথী এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা ছবির গান (সূত্রধর)।
|
| পাখির ছবি |
 |
ফি-বছর শীতে হিমালয় থেকে রকমারি পাখি নেমে আসে। তাদের জন্যই গত মার্চে ‘মন্দাকিনী ম্যাগপাই বার্ডওয়াচার্স’ ক্যাম্পের আয়োজন করেন পক্ষীপ্রেমিক যশপাল সিংহ নেগি। মন্দাকিনী-র ধারে সেই ক্যাম্পের জায়গাটি কয়েক মাস পরে উত্তরাখণ্ডের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংস হয়ে যায়। ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতার অতনু ঘোষ। ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করেন অতনুবাবু। তারই ফাঁকে ঘুরে ঘুরে পাখিদের ছবি তোলেন। সেই সব পাখির সঙ্গে এই প্রজন্মকে পরিচয় করাতে ৫ ডিসেম্বর সাড়ে পাঁচটায় গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় শুরু হচ্ছে তাঁর তোলা ৯২টি ছবির প্রথম একক প্রদর্শনী, চলবে ৭ পর্যন্ত (৩-৮)।
|
| আইনু |
 |
আইনু জাপানের প্রাচীন সম্প্রদায়। তাঁরা মনে করেন পশুপাখি, জল, মানুষ প্রভৃতি একে অন্যের পরিপূরক। তাঁদের নাচেও উঠে আসে এই বিশ্বাস। ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নে সম্প্রতি সল্টলেকের পূর্বাশা অডিটোরিয়ামে জাপানের বিরাটোরি আইনু কালচারাল প্রিজার্ভেশন সোসাইটি পরিবেশন করল আইনু নাচ (সঙ্গের ছবি)। সঙ্গে ছিল পুরুলিয়ার ছো নাচ। আয়োজনে বাংলানাটক ডট কম। এরাই আবার মুম্বইয়ের জঙ্গি হামলা স্মরণে পাবলিক রিলেশনস সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে আয়োজন করেছিল ‘২৬/১১ মিউজিক ফর পিস’। বিষয়-- ২৬/১১ অতীত, মালালা ইউসুফজাই ভবিষ্যত্।
|
| অ্যান ফ্রাঙ্ক |
অ্যান ফ্রাঙ্ককে সারা বিশ্ব চেনে তাঁর ডায়েরির জন্য। অ্যানের জন্ম ফ্রাঙ্কফুর্টে। ১৯৩৩-এ তাঁরা আমস্টারডামে আসেন, সে বছরেই নাতসিরা জার্মানিতে ক্ষমতায় আসে। নেদারল্যান্ড জার্মানির হাতে এলে বাড়তে থাকে ইহুদিদের ওপর অত্যাচার। দু’বছর লুকিয়ে থাকলেও ১৯৪৪ সালে তাঁরা ধরা পড়েন। ১৯৪৫-এ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ‘টাইফাস’-এ মারা যান অ্যান ও তাঁর বোন মার্গট। বেঁচে ছিলেন শুধু তাঁদের বাবা অটো ফ্রাঙ্ক, যুদ্ধ শেষে ফিরে তিনি খুঁজে পান অ্যানের দু’বছরের ডায়েরিটি। ১৯৪৭-এ ডাচ ভাষায়, ১৯৫২-য় ইংরেজি অনুবাদে দ্য ডায়েরি অব আ ইয়াং গার্ল সাড়া ফেলে দেয়। গত ৩০ নভেম্বর সন্ধেয় সিগাল ফাউন্ডেশন ফর দি আর্টস-এর প্রদর্শকক্ষে শুরু হয়েছে ‘অ্যান ফ্রাঙ্ক: আ হিস্ট্রি ফর টুডে’ নামক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। আছে বহু দুর্লভ ছবি। আমস্টারডামের অ্যান ফ্রাঙ্ক হাউস, ডাচ দূতাবাস ও পিসওয়র্কসের সহযোগিতায় এই প্রদর্শনী চলবে ১৩ পর্যন্ত, ৫-৭টা প্রতিদিন।
|
| লোকউত্সব |
শীতের কলকাতায় আবার লোক উত্সব। মুকুন্দপুরের লোকগ্রামে ৬ ডিসেম্বর উদ্বোধন হবে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের ১৯তম বর্ষপূর্তি উত্সবের। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে আসছেন লোকশিল্পীরা। ‘সুরে ছন্দে, মাটির গন্ধে’ এই উত্সবে ৬-৮ ডিসেম্বর রোজ সন্ধেয় দেখা যাবে এঁদের অনুষ্ঠান। থাকছে সাঁওতাল ও লিম্বু সম্প্রদায়ের নাচ, মানবপুতুল, তারের পুতুলনাচ, মারুনি নাচ, ভাঁড়যাত্রা, ছো, রণপা, ঝুমুর, আলকাপ, ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া ইত্যাদি। উত্সব প্রাঙ্গণে রোজই হাজির থাকবেন ‘ছিনাথ’ বহুরূপীর দল।
|
| আবৃত্তিশিল্পী |
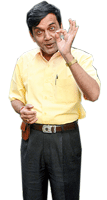 পেনেটি থেকে কলকাতা কত দূর? ‘সে এক দীর্ঘ লড়াইয়ের পথ,’ জানেন অরুময় বন্দ্যোপাধ্যায়। আবৃত্তি-শ্রুতি ও নাট্যচর্চায় পার করতে চললেন সাড়ে তিন দশক, কিন্তু আজও ভোলেননি সেই প্রথম দিনের ছোট্ট ছোট্ট পাওয়াগুলো। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আবৃত্তি শিল্প এবং তার প্রয়োগ (সপ্তর্ষি)। এমন গ্রাম্ভারি পুথির মতো নাম কেন? হো হো করে হেসে বললেন অরুময়, ‘বেশ একটা জলদগম্ভীর কণ্ঠ না হলে যেমন আবৃত্তিশিল্পে পাত্তা পাওয়া যায় না তেমন বইয়ের নামেও একটা ভারিক্কি চাল রাখতে হয়।’ মানুষটা কিন্তু মোটেই ভারিক্কি নন। পঞ্চাশের কোঠা ছুঁয়েছেন, কলকাতা দূরদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত, ঝুলিতে আবৃত্তি আর নাট্যপ্রযোজকের বেশ কয়েকটা সম্মান, তবু সেই মফস্সলের গন্ধমাখা সারল্যটা ছাড়েননি। ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মবর্ষে আবৃত্তিতে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। সেই সূত্রে সদ্য পার করলেন আবৃত্তির পঁচিশ বছর। প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘শৈলূষ’ সাংস্কৃতিক সংস্থার। এখন আবৃত্তিশিল্পের কলাকৌশল শেখানোর কাজ করতে চান। পেনেটি থেকে কলকাতা কত দূর? ‘সে এক দীর্ঘ লড়াইয়ের পথ,’ জানেন অরুময় বন্দ্যোপাধ্যায়। আবৃত্তি-শ্রুতি ও নাট্যচর্চায় পার করতে চললেন সাড়ে তিন দশক, কিন্তু আজও ভোলেননি সেই প্রথম দিনের ছোট্ট ছোট্ট পাওয়াগুলো। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আবৃত্তি শিল্প এবং তার প্রয়োগ (সপ্তর্ষি)। এমন গ্রাম্ভারি পুথির মতো নাম কেন? হো হো করে হেসে বললেন অরুময়, ‘বেশ একটা জলদগম্ভীর কণ্ঠ না হলে যেমন আবৃত্তিশিল্পে পাত্তা পাওয়া যায় না তেমন বইয়ের নামেও একটা ভারিক্কি চাল রাখতে হয়।’ মানুষটা কিন্তু মোটেই ভারিক্কি নন। পঞ্চাশের কোঠা ছুঁয়েছেন, কলকাতা দূরদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত, ঝুলিতে আবৃত্তি আর নাট্যপ্রযোজকের বেশ কয়েকটা সম্মান, তবু সেই মফস্সলের গন্ধমাখা সারল্যটা ছাড়েননি। ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মবর্ষে আবৃত্তিতে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। সেই সূত্রে সদ্য পার করলেন আবৃত্তির পঁচিশ বছর। প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘শৈলূষ’ সাংস্কৃতিক সংস্থার। এখন আবৃত্তিশিল্পের কলাকৌশল শেখানোর কাজ করতে চান।
|
|
|
|
|
| শতবর্ষে চিত্রনিভা |
 ছবি আঁকাই এক রকম তাঁর জীবনের পথ বদলে দিয়েছিল। ভগবানচন্দ্র আর শরত্কুমারী বসুর সবচেয়ে ছোট মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল নোয়াখালির জমিদার পরিবারে, তার আঁকা ছবি দেখে। সে বাড়িতে নিয়মিত আসত ‘প্রবাসী’, ‘মাসিক বসুমতী’-র মতো পত্রিকা। তাতে রবীন্দ্রনাথের লেখা আর নন্দলাল বসুর ছবির মধ্যে ডুবে থাকত বালিকা বধূ নিভাননী। শ্বশুরবাড়ির প্রশ্রয়ে চলছিল ছবি আঁকাও। সে সব দেখে শ্বশুরবাড়িতে সিদ্ধান্ত হল তাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানোর। স্বামী নিরঞ্জন চৌধুরী তাঁকে নিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে। তখন পুজোর ছুটি, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রাখলেন নিজের বাড়িতে। গান আর আঁকা শেখার জন্য ভৃত্য বনমালীর হাত দিয়ে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিতেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর কাছে। একদিন তাঁর আঁকা ছবি দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথই নাম পাল্টে দিলেন, নিভাননী হলেন চিত্রনিভা (১৯১৩-’৯৯)। শিক্ষাশেষে কলাভবনেই যোগ দেন শিক্ষক-পদে। তিনিই সেখানে প্রথম মহিলা-শিক্ষক। কিছু দিন পরে চিত্রনিভাকে ফিরতে হয় নোয়াখালিতে। সেখানেও গ্রামের মেয়েদের নিয়ে ছবি আঁকা আর গানের ক্লাস খুলেছিলেন। দেশভাগের পরে শিশুপুত্র ও কন্যাকে নিয়ে চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। ছবি আঁকা অব্যাহতই ছিল। স্বামীর কর্মসূত্রে কলকাতায়-- লেডি অবলা বসুর বিদ্যাসাগর বাণীভবনে শিল্পবিভাগের প্রধান হিসেবে সেলাই, আলপনা, চামড়ার কাজ, বাটিক শিখিয়েছেন বহু ছাত্রীকে। লিখেছিলেন একটি আত্মজীবনীও। ২৭ নভেম্বর শতবর্ষ পূর্ণ হল তাঁর, আত্মজীবনীটি প্রকাশের তোড়জোড় করছেন তাঁর কন্যা রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী চিত্রলেখা চৌধুরী। ছবি আঁকাই এক রকম তাঁর জীবনের পথ বদলে দিয়েছিল। ভগবানচন্দ্র আর শরত্কুমারী বসুর সবচেয়ে ছোট মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল নোয়াখালির জমিদার পরিবারে, তার আঁকা ছবি দেখে। সে বাড়িতে নিয়মিত আসত ‘প্রবাসী’, ‘মাসিক বসুমতী’-র মতো পত্রিকা। তাতে রবীন্দ্রনাথের লেখা আর নন্দলাল বসুর ছবির মধ্যে ডুবে থাকত বালিকা বধূ নিভাননী। শ্বশুরবাড়ির প্রশ্রয়ে চলছিল ছবি আঁকাও। সে সব দেখে শ্বশুরবাড়িতে সিদ্ধান্ত হল তাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানোর। স্বামী নিরঞ্জন চৌধুরী তাঁকে নিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে। তখন পুজোর ছুটি, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রাখলেন নিজের বাড়িতে। গান আর আঁকা শেখার জন্য ভৃত্য বনমালীর হাত দিয়ে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিতেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর কাছে। একদিন তাঁর আঁকা ছবি দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথই নাম পাল্টে দিলেন, নিভাননী হলেন চিত্রনিভা (১৯১৩-’৯৯)। শিক্ষাশেষে কলাভবনেই যোগ দেন শিক্ষক-পদে। তিনিই সেখানে প্রথম মহিলা-শিক্ষক। কিছু দিন পরে চিত্রনিভাকে ফিরতে হয় নোয়াখালিতে। সেখানেও গ্রামের মেয়েদের নিয়ে ছবি আঁকা আর গানের ক্লাস খুলেছিলেন। দেশভাগের পরে শিশুপুত্র ও কন্যাকে নিয়ে চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। ছবি আঁকা অব্যাহতই ছিল। স্বামীর কর্মসূত্রে কলকাতায়-- লেডি অবলা বসুর বিদ্যাসাগর বাণীভবনে শিল্পবিভাগের প্রধান হিসেবে সেলাই, আলপনা, চামড়ার কাজ, বাটিক শিখিয়েছেন বহু ছাত্রীকে। লিখেছিলেন একটি আত্মজীবনীও। ২৭ নভেম্বর শতবর্ষ পূর্ণ হল তাঁর, আত্মজীবনীটি প্রকাশের তোড়জোড় করছেন তাঁর কন্যা রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী চিত্রলেখা চৌধুরী। |
|
|
|
 |
|
|